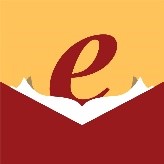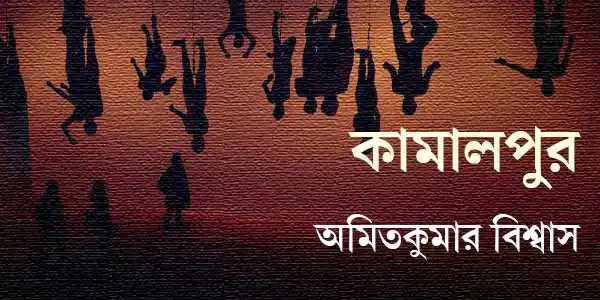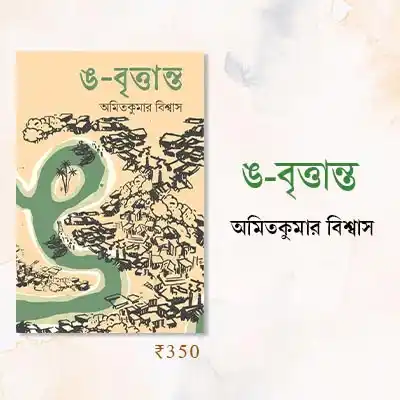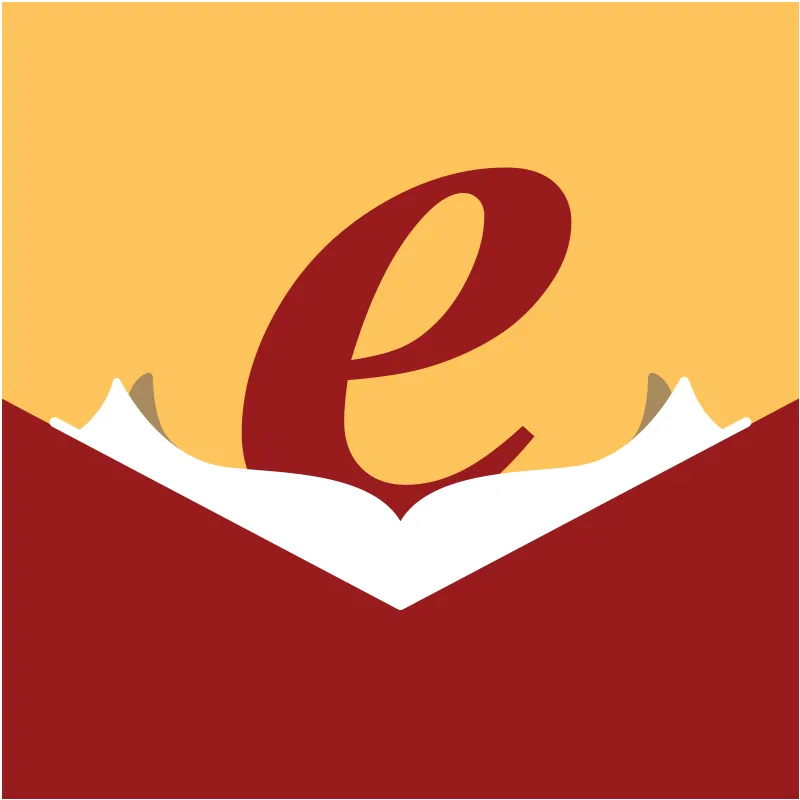বাইসার বিলমাঠে সন্ধে নামে অদ্ভুত। চাঁদ ওঠে। আকাশের নীলাভ ভাব কাটেনি তখনও। তখনও কুয়াশা জাপটে ধরেনি এই চঞ্চলা গ্রামপৃথিবীর শরীর। চরাচর ঝিঁঝিডাকে ভরে গেছে খুব। ঘরে ফেরা পাখিরা ডাকে। শেয়ালও ডাকে। ঘিলুর অন্ধকারে তখন প্রজেক্টর রুমের প্রবল ঘড়ঘড় শব্দ। পর্দায় শীৎকার। পরদায় উল্কাপাত, জোছনাপাত। সতেরোই শ্রেষ্ঠ রমণদা, সতেরোই শ্রেষ্ঠ! অথচ দ্যাখো লিঙ্গ থেকে বীর্য নয়, কান্না ঝরছে অঝোরে! প্রবল যৌন হতাশায় মাথাটা কেবলই ঝিমঝিম করতে থাকে বিলপাড়ে। এই বুঝি পড়ে যাব গোধূলির মায়াজলে।
পুরুষের সংগম সতেরোয় শ্রেষ্ঠ— বলেছিল রমণদা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিজি হোস্টেলের বোর্ডার তখন, আর চাগান পেলেই চলে যায় সোজা হাড়কাটায়। অজপাড়াগাঁয়ের মুখচোরা উঠতি যুবক যে গভীর জলের মাছ— এটা বুঝতে সময় লেগেছে আমাদের। গুরুগম্ভীর মানুষ। সারাদিন বইয়ে মুখ গুঁজে রাখে। বড়দার শ্বশুরবাড়ি গেলেই দেখেছি— উঠোনের পুবপাশে ছোট্ট চালাঘরে একাই থাকে। কলেজে পড়াকালীন ওপার বাংলা থেকে চলে আসে এপারে। বাগদহের কুরুলিয়া-সীমান্ত হেঁটে পেরিয়ে নতুন ঠিকানা তখন পুরাতন হেলেঞ্চা।
বড়দার শ্বশুরমশাই ও-দেশে রমণদার বাবার পড়শি ছিলেন একদা। সেই সুবাদে জানাশোনা। সরকারবাড়ি ছেলেকে পাঠানো। ছেলে এসে ক্লাস নাইনে ভর্তি হল হেলেঞ্চা বয়েজ হাইস্কুলে। ফলে বয়স যা ছিল উনিশ, তা কাগজ-কলমে হয়ে গেল চোদ্দো।
কলকাতা থেকে হেলেঞ্চা আসা-যাওয়ার মাঝে আমাদের বাড়িতে প্রায় রাতই থেকে যেত রমণদা। এমনকী স্নাতককালে বার্ষিক পরীক্ষাগুলি আমাদের ভিটেবাড়ি থেকেই দিয়েছিল। ট্রেনে যেত গোবরডাঙা হিন্দু কলেজ। প্রায় একমাস কাটিয়েছিল এখানে। চুপচাপ বইয়ে মুখ রেখে। কিন্তু সেই মানুষটিই কলকাতা থেকে ফিরে একেবারে অন্য প্রাণী! কথাবার্তায়ও কলকাতার টান।
‘কী-রে, কিছু করলি? গার্লফ্রেন্ডের কথা বলছি কিন্তু।’ এ-কথায় আমার তো দু-কান লজ্জায় লাল!
‘চুপ যে?’ আমাকে বোকাহাঁদার মতো মাথা নাড়তে দেখেই তার মুখে বিদ্রূপের হাসি। তারপরই শুরু। রমণদার গোপন পৃথিবীর পর্দা উঠতে থাকে এক-এক করে।
মাত্র সতেরো বছরে কীভাবে সবিতাদি-র সঙ্গে কাম চরিতার্থ করেছে, সেই অনুভূতি যে আজও চিরশ্রেষ্ঠ— তারা-ভরা চৈত্র ছাদে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে ঘোষণা দেয় রমণদা। ‘যে বয়সকে প্রকৃতি প্রস্তুত করেছে উপভোগের জন্য, উল্লাসের জন্য, সৃষ্টির জন্য— সেই বয়স আটকে আছে নিয়মের বেড়াজালে, ভাবতে পারিস? ফলে এর ফলাফল— হয় অবদমন, নয়তো কোনো নিষিদ্ধ উপায়।’ হা ঈশ্বর, আজ সাধুবাবাজির মুখে এ কী শুনছি আমি?
একদা হেলেঞ্চার গ্রামবাড়িতে পড়শি-প্রেমে টলমল রমণদা। বর্ষার পাটখেতে সে কী উদ্দাম যৌনতা! আকাশ থেকে বৃষ্টি নামে গুঁড়িগুঁড়ি। শুঁয়োপোকা লেগে লাল হয় শরীর। তবু ছাড়ে না কেউ কাউকেই। এরপর কলকাতা চলে গেলে বিরহ-বেদনায় শুকিয়ে কাঠ মালাবউদি। এমন যুবককে সভ্যতা কী বলবে? কোন লেখচিত্রে কীভাবে সংজ্ঞায়িত করবে তাকে? নিছক কামের দাস হয়ে পড়েই এ-কাজ— না কি অবদমনের ঘোরতর দাসত্ব অস্বীকার করে সে?
দুই
স্টেশানে আসতেই দেখি ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। সুদীর্ঘ সাপের মতো ধীরে ধীরে প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে ট্রেন। আমরা প্ল্যাটফর্মে থাকলে রানিং করা যেত। রমণদা বুঝি এমনই ঝুঁকি নিত একদা। ‘আরে পাঁচটা-সাতের বনগাঁ ধরবি, আর রানিং করবি না?’ কথাটা ঠিক সেই মুহূর্তেই বেজে উঠল একবার। প্রস্থানরত ট্রেন যেন ছায়াছবির পর্দা, তাতে তার অস্পষ্ট মুখটাও ভেসে ওঠে ছায়ার মতো সহসা। আহা রমণদা...
‘লাপ দে, লাপ দে লগাই!’
পোড়ামাটি-রঙা ডিজেল ইঞ্জিনের ট্রেন। কোনো এককালে দূরপাল্লার ছিল। পুরোনো হবার পর মেরামত করে ছোটোখাটো রুটে পাঠিয়ে দেওয়া আর কি। সিঁড়ি ঝুলছে নীচে পর্যন্ত। ফেরিওয়ালারা তো হামেশাই রানিংয়ে উঠে পড়ে। রোজকার অভ্যেস। বাকুও কিছুটা পারে। মাঝে মাঝে ট্রেনে চেপে এদিক-সেদিক যায় দেখি। কিন্তু আমি একটুও পারি না। ‘ক্যালায় আমার বিটি-মানষিরও অধম!’—
কথাটায় মটকা গরম হলেও মন ঝুঁকি নিতে নারাজ। ঝিকঝিক ঝুকঝুক করে বেরিয়ে যায় ট্রেন। দু-জনে ফিরে আসি পেছনের সাইকেল গ্যারেজে। সেখানে দাঁড়িয়ে সিগারেট। দু-টান দিয়েই আমার দিকে বাড়িয়ে দেয় বাকু। চোখে আমার বিস্ময়। রোমাঞ্চ। নিষিদ্ধ-তৃপ্তি। সেই প্রথম সিগারেট! আর প্রথম টানেই বাপ-মা ছাড়ানো কাশি! কাশির দমক সামলে দেখি খেঁকিয়ে হাসছে বাকু। দেখে বিরক্তি লাগে।
‘তালি কি ফিরে যাবি?’ কাশি থামলে বলি।
‘মেজদিবাড়ি যাতিই হবে ভাই, সে আজ যতই রাত হোক না ক্যান। এই ছাট্টিফিকেটগুলো কাল ওগে লাগবে।’
‘পরের টেরেন তো দেটটায়। তা এতসুমায় কোরবিডা কী?’ কথাটা শেষ হতে-না-হতেই আমার হাতঘড়ির দিকে তাকায় বাকু। কুড়ি টাকার ডিজিটাল ঘড়ি। বোলিদাপুকুর দরগার মেলা থেকে গত ফাল্গুনে কেনা। প্রতি সপ্তাহে পাঁচ মিনিট স্লো হয়ে যায়। সেজন্য ট্রেন মিস! আঙুল দিয়ে জোরে জোরে সুইচ টিপে টাইম ঠিক করি ঝটপট। একবার দু-মিনিট ফাস্ট হয়ে যায় তো, আর-একবার তিন মিনিট স্লো। গায়ের জোরে টিপতেই থাকি। শেষে তিনবারের-বার ও.কে.। খ্যাঁকশিয়ালের মতো ঘড়ির ডিজিট থেকে মুখ তুলে আমার ঘাড়ে হাত রাখে বাকু, তারপর ফিচেল হাসির সঙ্গে চোখ টিপেই বলে, ‘চল ভাই, উঁ! অ্যাঁ? হাঃ হাঃ হাঃ!’ সেইসঙ্গে কাঁধেও আঙুলের খামচা এসে লাগে। ইশারায় কিছুটা আন্দাজ করতে পারি। তবু না-বোঝার ভান করে বলি, ‘কুথায়?’
‘ক্যান, বিশ্বকর্মায়!’
‘নুন শো?’
ফের অবিকল সেই হাসি ছুড়ে বলে, ‘হ্যাঁ!’
‘হ্যাঁ’-এর লম্বা ‘অ্যাঁ’ আর আমাদের সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেয় না। সাড়ে এগারোটায় শো। আর মাত্র পাঁচ মিনিট বাকি! টগবগ টগবগ সাইকেল ছোটাই! বাকু রডে বসে। ‘তোকে রডে বসিয়ে বেল বাজাব...’। সামনে বসে বাকু ক্রিং ক্রিং বাজায় আর বেসুরো গায়। এ-গান কানে আসতেই আমার সারা-গা কেমন শিরশির করে ওঠে। শিরশিরানির অনুপুঙ্খ কম্পন লিঙ্গে, মূত্রনালীর পশ্চাৎ ও অগ্রভাগে, পায়ুছিদ্রমুখে, ওষ্ঠ ও অধরে, চোখের পর্দার ভিতরভাগে, হাতের আঙুলের ডগায়, পায়ের তলার অগ্রভাগের যে-অংশ ভূমি স্পর্শ করে, সেখানে। বিশেষ করে লিঙ্গ ও পায়ুছিদ্রের মধ্যবর্তী পেশিতে মৃদু আগুন লাগে। মিঠে ভয় ও আদিম রহস্যের আগুন। সে-আগুন ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র শরীরে। রোমে রোমে অনুভবের হলুদ মোমবাতি জ্বলে। মোম গলে ছড়ায়। ক্ষণিকের এই মহামূল্যবান অনুভব আত্মমৈথুনের মতন একাকী উপভোগের। এ-খবর ঈশ্বর রাখেন। মানুষের এই তৃপ্তি ঈশ্বেরকে জাগিয়ে রাখে অবিরাম। তিনি যে সৃষ্টিরও! আর সৃষ্টির প্রতিটি কণামুহূর্তে রয়েছে আণুবীক্ষণিক পুলকের স্পর্শ। এই তৃপ্তি মহাজাগতিক। বনবন করে ঘুরছে পুলক— অনন্ত স্নায়ুমণ্ডল জুড়ে— অসীম ছায়াপথে।
এবারে বাকুর গানে একটু বিরক্ত হচ্ছিলাম যেন। সাইকেলের ক্রিংক্রিং-ও কানে লাগছিল বড্ড। এইজন্যই বুঝি রসিক বাউলকে আলসে বিলপাড়ের মঞ্চ থেকে নামিয়ে দেয় পাড়ার বউরা! অথচ ‘তোমার আপন হাতের দোলে— দোলাও দোলাও দোলাও আমার হৃদয়...’ গাইলেই দোলনের মুখটা মনে পড়ে স্পষ্ট। মুখের পর আসে তার ঘাড়-পিঠ-বুক। তারপর কোমর ও নিতম্ব ছাড়িয়ে ঊরু বেয়ে নামতে থাকে থ্রি-ডি ছবিটা। পরনে লাল চুড়িদার। শোয়ার ঘরে পাজামা খুলে রেখে এসে দরজা দিয়ে হঠাৎ যখন কাকানের ঘরে ঢুকে আমার চাউনির সমান্তরালে হেঁটে যাচ্ছিল পালঙ্কের আড়ালে, হিপ বোন থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত তখন একটা সমদ্বিবাহু ত্রিভূজের দিকে হারিয়ে যায় আমার মন। সেদিনও আজকের মতো অনুভব সর্বাঙ্গে। নীরব গানে গানে এই অনুভব স্থায়ী হয়ে গেল বুঝি অন্তরে। আর গানের ওপাড়ে দোলন হাসছে, মুখ নাড়ছে, কপাল থেকে চুল সরাচ্ছে। তার প্রতিটি শ্বাসে বক্ষদেশের মৃদু উত্থান অনুভব করছি স্পষ্ট। আমার চোখকে কি পড়তে পারছিল দোলন? দোলনের বাবা-মা? কাকান? ভয় ভয় লাগছিল অনুভূতি ধরা পড়ে যাবার আশঙ্কায়। ‘নোটসগুলো কপি করা হয়ে গেলে ব্যাচে নিয়ে যাস খাতাটা’— বলেই ওঁর বাবা-মায়ের দিকে মুখ তুলে বলি, ‘আসি গো কাকিমা। কাকু আসি।’ তারপর ল্যাবদার মতো হাওয়াই চপ্পলে চ্যাটপ্যাট শব্দ করে দোতলা বাড়ির বাঁধানো উঠোন দিয়ে সাইকেল নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এগোলাম কাগুজেফুলে মোড়া প্রকাণ্ড গেটটার দিকে। দোলনকে পরদিন ফুলের কথা তুলতেই সে বলেছিল, ‘ওটা কাগুজেফুল না-রে হাঁদা, ওগুলোকে বোগেনভিলিয়া বা বাগানবিলাস বলে।’ সেই প্রথম ফুলের নামটা জানতে পারি দোলনের কাছে। আমাদের বিলপাড়ের কেউ কোনোদিন এর আগে এই নাম শুনেছে বলে মনে হয় না, অথচ অনেকের বাড়িতেই কাগুজেফুল নামে রয়েছে দিব্যি।
স্টেশান রোডেই বিশ্বকর্মা সিনেমা হল। বচ্চনের ‘মৃত্যুদাতা’ চলছে। পাঁচ বছর পর বচ্চনের ফেরা। দর্শকের আগ্রহ প্রবল। কিন্তু সাইকেল রাখতে গিয়ে গ্যারেজের মানুদা বিড়ি টানতে টানতে দেখি পাশের পানওয়ালাকে বলছে, ‘পানু, দ্বিতীয় সপ্তা তো আর জমলো না!’ অমিতাভের ভয়ংকরতম ভক্ত আমি, তাই কথাটা শুনে মন খারাপ হয়ে গেল। গুরুর বুঝি রাজকীয় প্রত্যাবর্তন হল না আর!
বচ্চনের বিরাট পোস্টারের নীচে খুদে পোস্টার। ‘হাসিনা চুড়েল’! সেদিকেই আড়চোখে চাওয়া মুহূর্তেই ধক্ করে উঠল বুক। বিশ্বকর্মার নুন-শোয়ে অ্যাডাল্ট সিনেমা চলে। এখানে টিকিট কেটে একবারই অ্যাডাল্ট সিনেমা দেখেছিলাম— ইলেভেনে ভর্তির পর-পরই। গোঁফ না-উঠলেও বেশ বড়োসড়ো চেহারা হয়ে গেছে আমার। গেটম্যান তাই আর আটকায় না। বেঁটে বাকুর তো পুরু গোঁফ সেই ক্লাস নাইন থেকেই। তাকে আর কে ঠেকায়? তো, টিকিট না-কেটে ঠিক ইন্টারভালের সময় টয়লেটে মিছিমিছি হিসি করে ঢুকে পড়তাম হলের মধ্যে। আসল ‘সিন’ তো ইন্টারভালের পরেই! কিন্তু আজ পরিস্থিতি ভিন্ন।
বাকুর সাফ কথা, আমার জন্যই নাকি ট্রেন মিস! ফলে আমাকেই টাকা বার করতে হয়। শুক্রবার। কলকাতা থেকে ফিল্মের ক্যান সবে হলে এসে পৌঁছল। শো শুরু হতে মিনিট কুড়ি লাগবে এখনও। সাড়ে তিন, সাড়ে তিন— পুরো সাত টাকা দিয়ে— হাফ-প্লেট করে— দুজনে খুড়োর বিখ্যাত সেই ‘ফাইভ স্টার হোটেল’ থেকে খাসির ছাঁট সাবড়ে দিলাম। সেখান থেকে উঠে কাউন্টারে গিয়ে ঝটপট দুটো টিকিট। আহ্, বহুদিন পর খুড়োর হোটেলে খেলাম! তা একমাস পর তো হবেই। হোটেলটা মানুদার বাবাই চালান। রেলের জায়গায় ছোট্ট ঝুপড়ি। তাতেই দুটো হাইবেঞ্চ। সারাদিনে টেবিল যেন খালিই হতে চায় না।
সিনেমা শুরু। বিশ্বকর্মার সত্তর এমএম ফিল্মের জন্য নির্মিত প্রকাণ্ড পরদার মাঝখানের কিছুটা অংশ জুড়ে পেছনের উঁচু প্রজেক্টর রুম থেকে জাদু-আলো এসে পড়ে। ঘড়ঘড় শব্দ হয় রিল ঘোরার। পর্দায় ছবি কাঁপে। উপর-নীচে দাগ পড়ে। দাগের কাটাকুটি খেলার মধ্যে শুরু হয় ‘হাসিনা চুড়েল’। আমি সমস্ত চেতনা দিয়ে কেবল একটা ‘সিন’-এর অপেক্ষায় থাকি।
এখানে ‘সিন’ বা ‘চলচ্চিত্রের দৃশ্য’ মানেই স্নানঘরে অর্ধনগ্ন হয়ে দক্ষিণী যুবতীদের শাওয়ার-স্নান। অথবা নদী থেকে আচমকা উঠে আসে ভিজে কাপড়ে। কিংবা ঘরে কাপড় ছাড়ছে, আর ওদিকে কি-হোলে ট্রিগার টিপে দেখছে কেউ। কিংবা রূপসী নারীটি সংগম-মুহূর্তে হয়ে গেল ডাইনি। কখনো ‘এ’ প্রতীক পাবার জন্য বি-গ্রেডের সিনেমায় গুঁজে দেওয়া হয় ন্যুডিটি। কখনো-বা তা কাহিনির সঙ্গে প্রাসঙ্গিক। কিন্তু তাতে শিল্পের ছোঁয়া লাগে না যেন কিছুতেই। যৌনদৃশ্য বা যৌন-আখ্যানে যদি সূক্ষ্ম শিল্পছোঁয়া না-থাকে, তবে তা নষ্ট হতে বাধ্য। কিন্তু যে-লোক তেরো বস্তা চাল ম্যাটাডোর থেকে নামিয়ে দোতলায় দিয়ে এল, দু-ঢোক চোলাই মেরে সে কি বুঝতে চাইবে শিল্পের সূক্ষ্ম চেতনা? অতএব প্রযোজক-পরিচালক বুঝে নেয় ঠিক কেমন সিনেমা বানাতে হবে। কাহিনির কোন কোন জায়গাগুলিতে টক-ঝাল-মিষ্টি দিতে হবে।
প্রবেশকালে অন্ধকার ছিল হল। কিন্তু চোখ অন্ধকার সয়ে ফেলতেই দেখি— পাড়াতুতো কালা কাকার পাশেই বসে আছি! টের পেয়ে সিটের মধ্যে সেঁটে আছে ছোট্ট মানুষটি। দু-হাতে মুখ ঢেকে টুক করে সরে পড়ি পেছনের সারিতে। এই প্রকার ছায়াছবিতে ভিড় কম হলে সাধারণত পেছন দিকের সিটে বসতে চায় দর্শক। সেদিন ভাগ্যিস ভিড় কিছুটা কম ছিল। টর্চম্যান বুঝি বুঝতে পেরে কিছু বলে না আর। কালা কাকার উচিত ছিল একটাকা বেশি দিয়ে ব্যালকনিতে বসা। ওখানে বয়স্ক পুরুষেরাই বসে সাধারণত। যাইহোক, সিনেমা শুরু হল, ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে রইলাম পর্দার দিকে। সিনেমা হিসাবে ‘হাসিনা চুড়েল’ খুবই নিম্নমানের। তবু ওই তিন-সাড়ে তিন মিনিটের দৃশ্যের জন্য দেড় ঘণ্টা চেয়ারে বসে বসে ছারপোকার কামড় খাওয়া। এখনকার মেইনস্ট্রিম হিন্দি সিনেমার একটা বিশেষ অংশ এদের কিন্তু হাফ ডজন গোল দেবে। যুগ পালটেছে, সিনেমায় জনগণের দাবিও পালটেছে। ক্যাসেট-সিডি-মেমোরি কার্ড পেরিয়ে যখন ইন্টারনেটের সহজলভ্য সভ্যতায় পা রাখল কালা কাকারা, যখন টিভির পরিবর্তে সব কিছুই মোবাইলের স্ক্রিন, তখন গোপন ঘরে তারা চাঙ্গা হয়ে উঠল ভারি। সতেরো কিংবা সত্তর— কী-বা আসে-যায় তাতে, যদি সক্রিয় থাকে লিঙ্গবাণ? কালা কাকার মেয়ে টুম্পা বলত, গায়েত্রীমাসির কাছে শরীরখেলার প্রতিটি স্নান প্রতিবারই ভীষণ নতুন নতুন লাগে তার। গায়েত্রী পাঁচ-ছ বছরের বড়োই হবে। বিয়ের আগ-পর্যন্ত থাকত ওই বাড়িতেই। ফলে দু-জনের মধ্যে সুখটানের কথা হত খুব। একজন সুদক্ষ সিনিয়ার সাঁতারু সাঁতার শেখার যাবতীয় টিপ্স জুনিয়ারকে দিয়ে আনন্দ পেত ভরপুর।
কী থেকে কীসে যে চলে যায় কাহিনি! কী আর বলি বলুন তো? কালা কাকা আমাদের বাড়িতে ঘরবেঁধে থাকত একদা। টুম্পা ছিল আমার ছোটোবেলার বন্ধু। পরে ওরা আমাদের বাড়ির পেছনে আলসে বিলের জমি কিনে দেড় কাঠায় টালিবেড়ার বাড়ি বেঁধে চলে গেলেও বন্ধুত্ব অটুট থেকে যায়। গায়েত্রীর কথাই ঘুরে-ফিরে আমার কানে আসে। ‘প্রতিবারই নতুন’— কথাটিতে ফুটতে থাকি আমি। মাঝে মাঝে মনে হয় টুম্পার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ি। টুম্পাও কি তেমন করে ভাবে কিছু? বুঝি না। ভালোবাসার ইঙ্গিত দিতেও ভয় পাই, পাছে কোথাকার জল কোথায় গড়ায়! যখনই বড়দা-মেজদা, বাবা ও হিটলার মায়ের কথা ভাবি, তখনই দমছাড়া দমকল হয়ে পড়ে থাকি এককোণে। এই টুম্পাকেই কিন্তু কাঁচামিঠে আম দেবার নাম করে ধর্ষণ করেছিল নিরঞ্জন ও আশিস। টুম্পার তখন সবে এগারো। ঘটনাটা জানাজানি হয়ে গেলে সেয়ানা আশু মহারাষ্ট্রে চটজলদি চম্পট দেয়, আর নিরা-বলদা ধরা খেয়ে মার খায় পাবলিকের হাতে। পরে সে-ও পলাতক। পুলিশকে আর জড়ানো হয়নি ঘটনাটিতে। বহু বছর পর আশু আলসের বিলে ফিরে এলে টুম্পার সঙ্গেই প্রেম হয়। পরে পালিয়ে বিয়েও। তবে নিরা যে কোথায় হারিয়ে যায়, কেউ জানে না। আশু বলে, মহারাষ্ট্রে ঘর বেঁধেছে সে। রঙমিস্ত্রীর কাজ করে। কল্পচোখে তাকে দেখি— বহুতলের গায়ে রুগ্ণ শরীর থেকে মাকড়সার মতো সুতো ছড়িয়ে পরের দেওয়ালে রঙ ভরছে জীবনের। আহা জীবন!
পর্দায় ‘হাসিনা চুড়েল’ কিংবা নিরঞ্জন দেউড়ি। পরদায় নানান রং। সব রঙ, সব মাকড়সার সুতো দেওয়ালে দেওয়ালে মিলেমিশে একাকার। দেওয়ালে এবারে বড়ে বড়ো করে ইংরেজিতে লেখা ‘ইন্টারভ্যাল’। এই শোয়ের ইন্টারভ্যাল পিরিয়ড খুবই কম, যতটুকু হলে হলকর্মীরা বাদাম-ছোলা নিয়ে রাউন্ড মারা শেষ না-করেন। এবং ম্যাটিনির মতো কিন্তু হলের অভ্যন্তরে ঝকঝকে আলো জ্বালানো হয় না। জ্বলে মৃদু নীল আলো। আলোয় দেখি আজ প্রায় সকলেই মাফলার বা চাদরে মুখ ঢেকে।
সিনেমায় ফিজা-লিজা দুই বোন। একবছর পর বড়োবোন ফিজা ফিরে এসেছে বাড়িতে— তারই মৃত্যুদিনে, যেদিন ধুমধাম করে লিজার জন্মদিন পালিত হচ্ছে হাভেলিতে। ফিজাকে দেখে সকলেই হতভম্ব। সকলে জানে চলন্ত ট্রেন থেকে ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যু হয়েছিল তার— উত্তর ভারতে, গভীর রাতে। পাহাড়ের খাদে পড়ে এই আত্মহত্যা— অভিমানে। এই মৃত্যুর নেপথ্যে রয়েছে তার স্বামী ভিকি— যে কিনা পাশের সিটে বসেছিল লিজার সঙ্গে। ভিকি এখন লিজার স্বামী। এইবার ফিজা ফিরে আসায় সম্পর্কের সমীকরণ কী হবে?
ফিজা এখন আগের মতো নেই আর। কেমন গুরুগম্ভীর। ভয় ভয় লাগে তাকে দেখে। তাকে এড়িয়ে চলে দু-জনে। কিন্তু এক মধ্যরাতে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা ফিজা-কে এড়িয়ে যেতে পারেনি ভিকি রয়। কী এক অমোঘ টানে পাশে আসে। ফিজার দু-হাত ধরে ক্ষমা চায়। হাউহাউ করে কেঁদে ওঠে ফিজা। এরপর দু-জনে হাত ধরে ফিজার ঘরে প্রবেশ করে। ঠিক এইখানেই ছিল সিনটা, ইন্টারভালের পরেই। ঘরে মৃদু লাল আলো। একে একে পোশাক বাতাসে ছড়িয়ে দিচ্ছে ফিজা। এখন সম্পূর্ণ স্পষ্ট তার রক্তিম শরীর। ভিকিরও। শুরু হয় ফোর-প্লে। তবে উভয়ের নিম্নাঙ্গ না-দেখিয়েই। তখনকার সিনেমাহলে ওইটুকুই শ্রেষ্ঠ। আর তাতেই কিনা বাকু জিপ খুলে চোখমুখ কেমন করতে থাকে। মৃগীতে ধরেছে যেন। মুখ থেকে কেমন শব্দ বের হয় বাকুর। মনে হয় বাকুর দেখাদেখি সামনে পেছনে ডাইনে বাঁয়ের সকলেই জিপ খুলে ফেলছে। কালা কাকাও। সকলের নজর পর্দায়। আমি পায়জামা পরে। দড়িতে টান মারতে হাত কাঁপে। পর্দায় ফিজা-ভিকির তুমুল সংগম, তবে ফ্রন্টাল নুডিটি সরিয়ে। আমার পায়জামার দড়ির একমুখ ফিজা তার নিজের মুখে পুরে আর-একমুখ তার তুলতুলে হাত দিয়ে টান দিলেই আমি আনন্দ-উত্তেজনা ও ভয়ে কাঠ হয়ে যাই! আহ্, প র দা প র দা প র দা...তুমিই ব্রহ্ম, তুমিই শ্রেষ্ঠ! আহ্ আহ্ আহ্ পরদা— এ পৃথিবীর বুকে সতেরো বছর নেমে আসুক ধীরে! বলতে বলতেই যেন সমবেত কামানপাত! যেন পর্দার সকল রঙিন মায়াবী দৃশ্য মুহূর্তেই থকথকে জোছনায় ভরে যায়। এ-দৃশ্য বাস্তব, না কি অলৌকিক? ঠিক তখনই কাম চরিতার্থ হলে প্রকৃতরূপ ধারণ করে ফিজা! কামানপাত, জোছনাপাত সরিয়ে মুহূর্তেই পরদার রং ফেরে। মুহূর্তেই সুন্দরী ফিজা হয়ে যায় বীভৎস ডাইনি। ভয়ে চিৎকার করে ভিকি। ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হয় তার কণ্ঠ থেকে। চিৎকারে ছুটে এসেছিল লিজা। এই দৃশ্যে সে পালিয়ে যায় হাভেলি থেকে। পরদিন হাভেলির উঠোনে ভিকির লাশ পড়ে থাকতে দেখে গ্রামের উত্তেজিত লোকজন ঢুকে পড়ে হাভেলিতে। তাদের হাতে খুন হয় ফিজা। এরপর আগুন লাগিয়ে দেয় গোটা হাভেলিতে। আগুন থামলে দেখা যায়— একটা পোড়া ও ভাঙা হাভেলির মেঝেতে পড়ে আছে আধপোড়া চুড়েল। হাত ও পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। এবারে পোড়োবাড়ির দৃশ্য। এবারে বনের মাঝে পোড়োবাড়ির দৃশ্য। সন্ধ্যা নামে। একটা বিকট হাসির মধ্যেই দৃশ্যটা অ্যান্টি-ক্লোকওয়াইজ পাক খায়। পাক খেতে-খেতে একটা চরকি হয়ে যায়। চরকিটা এক শিশুর হাতে। সে দাঁড়িয়ে সেই পোড়ো হাভেলির সামনে। তার দাদু ঝপ করে হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে যায় উঠোন থেকে বাইরে। হিন্দিতে শিশুটি জিজ্ঞাসা করে, ‘দাদু, কী এটা?’
‘এটা ডাইনির বাড়ি। আমি যখন তোর মতো ছিলাম, তখন তাকে মেরে ওই হাভেলিতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়।’
‘তুমি দেখেছ?’
‘হ্যাঁ।’
‘গল্পটা বলো তবে...’
‘কাল বলব।’
‘না, আজ!’
‘আরে দাদুভাই, কাল শুনিস।’
‘না, আজ বলবে তুমি, না কি আবার দৌড়ে চলে যাব ডাইনির বাড়িতে?’
‘বড্ড বেয়াদব আজকালকার বাচ্চারা। নে শোন তবে—’
সিনেমাটা শুরু হয়েছিল ঘুরন্ত চরকি হাতে নাতি ও দাদুর গল্প দিয়েই। জানি, দাদু সংগম দৃশ্যটা ‘তখন তাদের প্রেম হল’ বলেই কাট করে ঢুকে গেছেন ডাইনির দৃশ্যে। এই এগারোর শিশু আর পাঁচ-ছ বছর পর উপলব্ধি করবে দাদুর ‘কাট’-এর মাঝে গল্পটুকুর উত্তাপ, স্বপ্নঢেউ ও জোছনাপাত।
কিন্তু গল্পে লিজার ঠিক কী হল? নাতির প্রশ্নে দাদু জানিয়েছিল, লোকে বলে আলেপ্পি থেকে পালিয়ে বম্বে গেছে লিজা। ঘর বেঁধেছে। আবার কেউ কেউ বলে লিজাকে আগেই নাকি খুন করে গুম করেছিল হাভেলিতে। ফলে তারা তিনজন আজও পরিত্যক্ত ওই হাভেলিতেই থাকে— ভূত হয়ে, সকল জীবিত চোখের আড়ালে। এ যেন দরজার এপাশ থেকে ওপাশে যাওয়া। মৃত্যুর পরও আর-একটা জগৎ। সেখানে তিনজন তিনজনকে পেয়ে আনন্দ যেন ধরে না আর! এবারে নির্জন অরণ্য-হাভেলি আর ওরা তিনজন— সুখে কেটে যায় সীমাহীন দিন-রাত্রি। এমন হ্যাপি এন্ডিংয়ে তৃপ্ত হয় দর্শকমন। হাততালিও পড়ে। আজগুবি সিনেমা। তবে ভূতপ্রেমিদের ভালো লাগবে। ভালো লাগবে দাদুকে করা নাতির প্রশ্ন, ‘কিন্তু ডাইনি কীভাবে ভূত হয়, দাদু?’
‘হয়রে হয়, মানুষ যখন বিজ্ঞানের চর্চা কম করে, তখনই হয়।’
‘আমি তাহলে বিজ্ঞান-চর্চা করব, ফলে মানুষ আর ডাইনি হবে না। আর ডাইনিও শেষে ভূত হবে না! ভালো হবে, তাই না দাদু?’
‘ভালো মানে ভালো? খুব ভালো হবে!’
আলেপ্পি থেকে বম্বে গেছে লিজা? না কি সে ওই বাড়িতেই খুন? মাথায় ঘুরছিল প্রশ্নটা। ভুলেই গেছিলাম এটা ভূত ও ডাইনির আজগুবি সিনেমা, আজগুবি গল্প। কিন্তু আজগুবি হলেও মস্তিষ্ক তা দেখেছে। কিছু কিছু দৃশ্য কিছু কিছু কাহিনি নিজের মতো করে রেকর্ড করেছে গ্রে ম্যাটার। ফলে যতই চেষ্টা করি না কেন, মাথায় তা ঘুরপাক খাবেই। কোথায় এই মুহূর্তে বাকুর মেজদিবাড়ি গিয়ে আয়েশ করে পুকুরের মাছ খাব, আর কোথায় কি না আলেপ্পি, বম্বে, ভূত, পেত্নী, ডাইনি-পৃথিবীর মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে বর্তমান চেতনের কাহিনি-উপকাহিনিগুলি!
কাহিনি-উপকাহিনি, দৃশ্য-রং-সংগীত, গান কিংবা কবিতার পঙ্ক্তি— সবই প্রতি মুহূর্তে ঘুরপাক খেতে থাকে আমাদের ধূসর অংশে। ফলে প্রতিমুহূর্তে সংকট, দ্বন্দ্ব, সন্দেহ। এমন মানুষকে কড়া প্রশিক্ষণ দিয়ে দিয়ে কারখানার উপযোগী করে তোলে পুঁজিবাদী সভ্যতা। ‘এমন প্রশিক্ষণ দাও যে, মানুষজন কল্পনা করবে না, গল্প পড়বে না, কবিতা পড়বে না, বরং সে কেবলই বলদের মতো লাঙল টানবে, গাড়ি টানবে।’— অমূল্যবাবু বলতেন। তখন তাঁর আশি। দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন। সে-যুগের ডাবল এম.এ। কবি কেশবলাল বিদ্যাপীঠের প্রাক্তন সহকারি প্রধান শিক্ষক। আমরা বাংলা ও ইতিহাস টিউশানি পড়তে যেতাম তাঁর কাছে। দৃষ্টি নিয়ে কথা উঠলেই বলতেন, ‘আলো মনে থাকে, চোখে নয়। তোমাদের রেখে আমি চলে যাচ্ছি শীঘ্রই। পৃথিবীতে তোমরা আলোর কথা বলে যেয়ো অন্তত।’
নিরঞ্জন ও ছোটোবোন লিজার কাহিনির মধ্যে যৎসামান্য মিল রয়েছে। দু-জনেই বম্বে গেছে। সেখানে ঘর বেঁধেছে— খবর রটেছে তেমনই। এখন লিজার কাহিনি কেবল কাহিনিই। ফিল্মি কাহিনি। অপরদিকে নিরঞ্জন একটি রক্ত-মাংসের বাস্তব চরিত্র। আলসে বিলপাড়ের চরিত্র। এই মিল বড়োই কাকতালীয়। আসলে মাঝে মাঝে মনে সন্দেহ জাগে, ভোলার মতো সে এই পাড়াতেই গুম হয়ে যায়নি তো?
পশ্চিম আলসে বিলের একদা মুকুটহীন সম্রাট নায়েব মণ্ডলের যুবক ছেলে ভোলাকে তারই দুই বন্ধু গণা ও নগা খুন করে তাঁতিবুড়ির গর্তে পুঁতে রেখেছিল দেড় বছর। লাশ অর্থাৎ কঙ্কাল উদ্ধার হয় ১৯৯১ সালের বর্ষায়। মাঝে মাঝে খবর আসত, সে-ও বম্বে গেছে। এমনকী ভুয়ো চিঠি আসত বাড়িতে, ‘সামনের পুজোয় আসছি।’ চালিভ্যান চালক শংকর ঘরামি সেই যে যদুদাদের আমগাছ থেকে শেকল খুলে নিজের ভ্যান নিয়ে এক শীতের সকালে চলে গেল, আর ফিরল না এ-জীবনে। তারই বন্ধু বনগাঁ-শেয়ালদা রেললাইন-পাড়ের মহাদেবদা, একদা যে কিনা আলসে বিলপাড়েই থাকত, ভ্যান চালাত, কিছুদিন আগে বলল, ‘শংকর জলপাইগুড়িতেই!’
‘তুমি কি নিজের চোখে দেখেছ, দা?’
‘না ভাডি, তবে ভগার মুখি শুনিচি।’
‘আর ভগা?’
‘ভগার কাছে শুনতি হবে তালি!’
কী আশ্চর্য এই জীবন, পরানের বন্ধু হারিয়ে যায় পৃথিবী থেকে, বহুকাল পর তার খোঁজ পাওয়ার ন্যারেটিভ বিষয়ে ঘোর উদাসীন তারই বন্ধুরা! এমন ন্যারেটিভ চালু থাকায় বিলপাড় থেকে কেউ কোথাও গিয়ে ফিরে না-এলে সন্দেহ দানা বাঁধে। শুধু পুরুষ নয়, এ-পাড়া থেকে মেয়ে-বউও হারিয়ে যায়। কলকাতা-দিল্লি-বম্বে এমনকী দুবাইয়ের বেশ্যা হয়ে চলে যায় তারা। কিংবা হরিয়ানা-পাঞ্জাব থেকে এসে মেয়ের পরিবারকে টাকা দিয়ে ‘মেয়ে’ কিনে নিয়ে যায় ‘বউ’ হিসেবে। এ-পাড়ায় সস্তায় বউ ও বেশ্যা পাওয়া যায় ভরপুর। অতিসস্তায় শ্রমিকও পাওয়া যায় ঢের। বিলপাড়ের উদ্বাস্তু মানুষেরা দেশভাগের পর গত সত্তর-পঁচাত্তর বছর ধরে কেবলই সংগ্রাম করে যাচ্ছে দু-পায়ে দাঁড়ানোর জন্য। দু-একজন ব্যতীত সকলে আজও দুটো দানাপানির জন্য ঘোর সংগ্রামে। তাই চলে যায় বম্বে, মাদ্রাজ, কোয়েম্বাটুর, দুবাই কিংবা দোহা। কেউ কেউ বহুযুগ পরে ফিরে আসে। পাড়ায় তখন হইচই পড়ে যায়। নিজের বউ-বাচ্চা ফেলে নিখিলের বউ নিয়ে বিকাশ পালিয়ে গেছিল আসামে। সাত বছর পর এক শীতসন্ধ্যায় নিজের উঠোনে ফিরে এলে বেবি ক্যাঁৎ করে লাথি মারে তলপেটে! অমনি বিকাশ পড়ে যায় গোলপোস্টের পেছনে শিবেই গাছির উপুড় করা সারি সারি ঠিলের ওপর। ঠিলে ভাঙে। আরও লোক জড়ো হয়। বিকাশ আর ওঠে না দেখে লোকজন ধরাধরি করে তোলে। বিকাশের মুখে রক্ত। হাসপাতালে নিয়ে যায় বিলপাড়ের বখাটে ছেলেপুলেরা। হাসপাতালের বেডে ক-দিন শুয়ে থেকে থেকে একেবারে শুয়ে পড়ে বিকাশ। কিডনি দুটো শেষ হয়ে গেলে ক্যাঁৎ করে লাথি মেরে আসাম থেকে পাঠিয়ে দিয়েছে বিলপাড়ের খেলার মাঠে। ওহ্ বিকাশ বৈরাগী— তুমি কিনা বিলপাড়া তরুণ সংঘের স্ট্রাইকার! আমাদের মারাদোনা! বল নিয়ে শাঁ শাঁ করে বিপক্ষ খেলোয়াড়দের একের পর এক কুপোকাত করে ঢুকে যাচ্ছ বিপক্ষ শিবিরে। এইবারে বাঁ-পায়ের কিক্! গোওওওওল! তোমার খেলা দেখে গোপালনগরের বেবি চক্রবর্তী প্রেমে পড়ল। নমশূদ্র পরিবারে বিয়ে-বিষয়টি ঠাকুরবাড়ির কেউ মেনে নিল না। তবু গরিবের ঘরে ছপ্পর ফাড়কে প্রেমের জয়জয়কার। গোওওওল! আজ তুমি হারাধন মণ্ডলের রজনীগন্ধার খেত থেকে তুলে-আনা ফুলের সাজে বড়েই সেজে উঠেছো এই কুয়াশাভরা শীত-সকালে! মৃতবাড়ির ধূপের গন্ধ বুঝি-বা সম্পূর্ণ ভিন্ন— ট্র্যাজিক পরিমণ্ডল সৃষ্টিতে অনবদ্য। তুমি সেজে উঠেছো বিকাশ বৈরাগী— গোলপোস্টের পাশে— দড়মা-টালির ছোট্ট ক্লাব-প্রাঙ্গনে। ঈশ্বরের পায়ে পায়ে ফুটবল হয়ে এখন তুমি চলেছো কোন সে অজানা সুদূরের ‘গোল’-পথে? এই নায়েব মণ্ডলের গল্প, এই শংকর দেউড়ির গল্প, এই বিকাশ বৈরাগীর গল্প ফের অন্য কোথাও হবেখন। এদের গল্প ফুরোয় না সহজে।
ডাইনি, ভূত ও সম্ভোগের পৃথিবী ছেড়ে আমরা এসে পড়লাম বনগাঁ রেলস্টেশানে। পথে বাকু ফের ধরেছিল বেল বাজানোর গান। থামালাম তাকে, আর গাইলাম ‘দোলাও দোলাও দোলাও— আমার হৃদয়!’ বাকু সাইকেলে বসেই জিলিপির মতো শরীরটা ঘুরিয়ে মুখের দিকে চেয়ে যা একটা ফিচেল হাসি দিল মাইরি— এতকাল পরেও তা মনে আছে স্পষ্ট! মনে পড়ে, এরপর আমাকে গম্ভীর মুখে দেখলেই বেসুরো গলায় মুখে বাতাস ভরে হাত দু-খানা শূন্যে তুলে গাইত— ‘দোলাও দোলাও দোলাও— আমার রি-দ-য়।’ গানের ‘হৃ’ আমাদের মুখে কখনো ‘হৃ’ হয়নি সেই বয়সে।
স্টেশানে এসে দেখি বাকুর কাছে টিকিট কাটার পয়সা নেই। তাহলে? সে বলে, ‘ভ্যানে যাবারও তো পয়সা নাই!’
‘তালি?’
‘সাইকেলডা নিয়ে চ দিন।’
‘টেরেনে?’
‘হ্যা-অ্যা-অ্যা।’ তার মায় আমার এই ‘হ্যাঁ’-তে কোনো চন্দ্রবিন্দু নেই। সঙ্গে আরও বলে, ‘দজ্জার পাশে রাখার জায়গা আছে। চ।’
‘আর টিকিট?’
‘আরে আমরা কি আর রানাঘাটে নামবো নেকি? গাংনাপুরি টিকিট লাগে না!’
আমার পুরোনো হিরো জেট এখন ট্রেনে। কামরার টয়লেট-সেকসান তুলে দিয়ে সমান করে দিয়েছে রেলকোম্পানি। সেখানে ঝুড়ি-ধামা-বস্তা রাখে গ্রামজনেরা। আমরা সাইকেল রাখলাম। এই রুটে খুব একটা লোক চলাচল করে না। ফলে চাপ নেই।
এ রুটের কয়েকটি স্টেশানে কোনো প্ল্যাটফর্ম নেই। সিঙ্গেল লাইন। সাতবেড়িয়া হল্ট। খেলার মাঠের পাশে ট্রেন দাঁড়ায়। দু-একজন সবুজ মাঠের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে উঠে পড়ে। যেন ফুটবল খেলা ছেড়ে আচমকা উঠে-আসা। এরপর বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গোপালনগর। তারপর আকাইপুর, মাঝেরগ্রাম।
মাঝেরগ্রামে দুটো প্ল্যাটফর্ম। এখানেই ক্রসিং। এর পশ্চিমের প্ল্যাটফর্মটি বনগাঁ মহকুমা অর্থাৎ উত্তর চব্বিশ পরগনা এবং পুবেরটি নদিয়া জেলার মধ্যে পড়ে। দু-পাশেই বিস্তীর্ণ অরণ্যদেশ, চাষের মাঠ। তারই ফাঁকে আমরা— ট্রেনে। মাঠসমুদ্র সরষেফুলে হলুদ হয়ে আছে। মাত্র বাইশ কিলোমিটার পথ, যা এখন কুড়ি মিনিট লাগে, লাগল প্রায় পঞ্চাশ মিনিট। আসলে মাঝেরগ্রাম ক্রসিংয়েও তো দাঁড়ানো ছিল এর মধ্যে অনেকটা সময়।
অবশেষে আমরা দুপুর আড়াইটে নাগাদ গাংনাপুরে নামি। পেট তখন চোঁ চোঁ ডাকছে। এদিক-ওদিক তাকাই। স্টেশানের কোনো এক গুমটি থেকে ডিম ভাজার ঘ্রাণ আসছে তীব্র! বাকুর মুখের দিকে হাজার বছরের করুণ মুখ নিয়ে নীরবে চেয়ে থাকি। সে বলে, ‘মেজদিবাড়ি গিয়ে খাবো। তুই চালা।’ আর তাই আমি চালাই। খিদের টানে গতি যতই বাড়াতে যাই, ততই যেন পিছিয়ে পড়তে থাকি।
মেঠোপথ। পথ এগোয়। এগোয় আর এগোয়। গ্রাম ছেড়ে চাষের মাঠ। চাষের মাঠ ছেড়ে আবার গ্রাম। গ্রাম ছেড়ে আবার চাষের মাঠ। মাঠের মাঝে চওড়া আল। আল ছেড়ে আবার গ্রামের মেঠোপথ। কামালপুর আর কিছুতেই আসে না! মনে হয় বন্যার জলে গোটা গ্রামটাই ভাসতে ভাসতে চলে গেছে দূরে! কিংবা আমরা এগোচ্ছি না, বরং ক্রমেই পিছিয়ে পড়ছি।
উঁচু-নীচু পথ। বার বার সাইকেলে চেন পড়ে। চেন তুলতে গিয়ে হাত কালি-কালি হয়ে যায়। বাকু বলে, ‘ফাঁসুড়ে-বটতলা পেরোলিই কলাম মেজদিবাড়ি!’ শুনে প্যাডেলে গতি আরও বাড়ে।
যেতে যেতে ফাঁসুড়ে বটতলার অনেক কিস্সা শোনায় বাকু। তাতে গা ছমছম করে এই নির্জন দুপুরে। ভয়ে ভয়ে পার হই। কিন্তু হায়, বটতলা পেরোতেই ফের চেন পড়ে! যত হুটোপাটা করি, ততই দেরি হয়। শেষে জয় মা বলে কোনোরকমে সেট করে বাকুকে বলি, ‘হোই ব্যাকাই, তা তুই এট্টু চালা!’ কিন্তু রডে বসে-থাকা আরও যে যন্ত্রণার। তার উপর আমার মতো শুটকো পাছার। তাই একটু যেতে-না-যেতেই বলি, ‘দে— রাখ রাখ, আমি চালাই।’ বাকু আমার মতো খ্যাংড়াকাঠি নয়, ফলে বসে আরামই পায় নিশ্চয়ই।
যেতে যেতে যখন সঠিক পথের খোঁজ করছি, গ্রামবুড়োদের কেউ কেউ জানিয়েছেন— সোজাসুজি এই পথ ধরে সামান্য পশ্চিম-ঘেঁষা উত্তরে গেলে ঠিক দু-কিমি পরেই দেবগ্রাম ফরেস্ট। কোনো এক সুদূর অতীতের দেবলগড় সভ্যতা এটি। আর এমন ঘুরপথে দিদিবাড়ি দশ কিমি তো হবেই!
দেবগ্রাম ফরেস্ট? দেবলগড় সভ্যতা? ইতিহাসগ্রন্থে সিন্ধু সভ্যতার কথা পড়েছি। হরপ্পা-মহেঞ্জোদাড়োর কথা পড়েছি। বইতে ছবিও দেখেছি কিছু কিছু। ইটের স্তূপ, স্নানাগার, হাতকাটা পুরোহিত, নগ্ন নর্তকী। ‘নগ্ন’ শব্দটির প্রতি শিহরণ যেন সুতীব্র। দেবগ্রামেও কি তবে তেমনই কিছু আছে? কই আমাদের ইতিহাস স্যারেরা তো তেমন কিছুই বলেননি কখনো! যদি বনের মধ্যেই চাপা পড়ে থাকে সভ্যতা, তাহলে আমিই তো উদ্ধার করতে পারি। আবিস্কার করতে পারি লুকিয়ে থাকা সভ্যতাকে! হয়তো বনের মধ্যেই ইটের পাঁজা। সেখানে ভয়ংকর-সব প্রাণী। সেটা পেরোলেই বিশাল এক পোড়ো হাভেলি!
হাভেলির কথাটি মাথায় আসতে-না-আসতেই মন ‘হাসিনা চুড়েল’-এ ঢুকে পড়ল সহজে। চেতনাও শর্টকাট চায়। এই মুহূর্তে খুব দ্রুত সে পৌঁছাতে পারে হাভেলিতে। আবার হাভেলির কথা মনে আসতেই দেবলগড় সভ্যতায় কী কী আবিস্কার করতে পারি— তার একটা দীর্ঘ তালিকা তৈরি হচ্ছিল মস্তিষ্কে। একটা লাশ নাচঘরের ঠিক নীচেয় কবর দেওয়া। এই সেই লিজা বোধহয়। তার করোটি নিয়ে কম্পিউটারে ফ্রেমিং করতে দিয়ে একটা ‘মুখ’ পেলাম যা অবিকল সিনেমার লিজার মতো। কার্বন টেস্টেও বয়স ও ঘটনাকাল ঠিকঠাক। তাহলে কি এইখানেই ঘটেছিল ঘটনাটা? আরে, এমন তো আখছাড়ই হয়। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ‘হিঙের কচুরি’ লেখেন, আর তা হয়ে যায় উত্তম কুমার-সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় অভিনীত বাংলা ছায়াছবি ‘নিশিপদ্ম’ কিংবা রাজেশ-শর্মিলা অভিনীত হিন্দি ছায়াছবি ‘অমর প্রেম’। আচ্ছা, ক-জন জানে এই কাহিনি আমাদের বনগাঁর? ওই বনগাঁ পৌরভবনের বিপরীতে, যেখানে বিবেকানন্দ কোচিং সেন্টার আছে, যেখানে এখনও কিছু ব্রিটিশ আমলের পুরোনো বাড়ি দেখা যায়! আর পুষ্প নাম্নী মেয়েটিও তো বিভূতিভূষণের পরিচিত ছিল। ছায়াছবির পুষ্প, গল্পের কুসুম আর বাস্তবের হাজু। গোপালনগরের হাজু। গল্পটা আমায় রঞ্জনদার ভায়রা-ভাই বিভূতি-পড়শি অঞ্জনদা বলেছিলেন। অঞ্জনদার বাবা অনন্ত ডাক্তার ছিলেন বিভূতিভূষণের ছাত্র। বনগাঁয় বিভূতিভূষণের রোজকার সান্ধ্য আড্ডা লিচুতলা ক্লাব থেকে হাজুদের নিষিদ্ধ পল্লিটি ছিল ঢিলছোঁড়া দূরত্বে। ব্রিটিশ ও বাবুদের খুশি করতেই কিনা ইতিহাসের বনগ্রামে হাজুরা ওইখানে! কিন্তু হাজুই যে গল্পের কুসুম— এমন তো গল্পকার কোথাও বলে যাননি! তা ছাড়া গল্পের পটভূমি তো কলকাতা।
তাতে কী— তা-বলে হাজু কুসুম হতে পারে না? অঞ্জনদা লোকটা তথ্যে ততটা বিশ্বাসযোগ্য নন। দক্ষিণ বিলপাড়ে রঞ্জনদার বাড়িতে এলে সে যা গাবান দেয় না! এইসব পুরাকাহিনি, এইসব ফিল্মিকাহিনির সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে অবশেষে আমরা কামালপুরে এসে পৌঁছাই।
কেতাব-ই’র ব্লগজিন বিভাগে লেখা পাঠাতে চান? মেল করুন blogzine.ketabe@gmail.com-এ। মেলের সাবজেক্ট লাইনে লিখুন ‘কেতাব-ই ব্লগজিনের জন্য লেখা’।
তিন
তাল-খেজুরে সাজানো স্বপ্নের গ্রাম কামালপুর। গ্রামদৃশ্যের শৈল্পিক সূক্ষ্মতা বৃদ্ধিতে তালখেজুরের স্পর্শ অনস্বীকার্য। রাস্তার দু-পাশে, জমির আলে, খাল ও পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে আছে গাছগুলি। আম-জাম-কাঁঠালের উঁচু-নীচু ছবি দেখি চরাচরে— যেন সমতল ভূমির একখণ্ড দৃশ্য-পাহাড়! গাছিরা গাছ কাটে। রস পাড়ে। গুড় জ্বালায়। বাকুর জামাইবাবুও একজন ভালো শিউলি। তিনি হাটে গেছেন। ফিরবেন রাতে। বাড়িতে বাকুর দুই কিশোরী বিয়ান আছে— চন্দ্রা ও চঞ্চলা। ট্রেনে আসতে আসতে বাকু ওদের কথাই বলেছিল বলছিল।
এসেই আগে খেয়ে নিয়েছিলাম। ফলে শরীর চনমনে। চন্দ্রা-চঞ্চলা সন্ধের কিছু আগেভাগে রস পাড়তে বাকুকে নিয়ে যায় বাইসা বিলের পাড়ে। আমাকেও ডাকে চঞ্চলা। না না করেও যাই পিছু পিছু। চাঁদসন্ধে নেমেছে চরাচরে। চঞ্চলা ও আমি দাঁড়িয়ে পাশাপাশি। যেন হাওয়া দিলেই গায়ে গা লেগে যাবে মুহূর্তেই! চঞ্চলার শরীর থেকে জিরন রসের ঘ্রাণ ছড়ায় কেবল। মিশে যায় আমার মনে, আমার সতেরোর শরীরে। চন্দ্রা চুড়িদারের উপর গামছা পেঁচিয়ে নেয়। চড়চড় করে উঠে পড়ে খেজুর গাছে। নামিয়ে আনে ঠিলে। খেজুরের নালি থেকে রস পড়ে নীচে। জিভ পাতে বাকু। অমনি চোখে এসে পড়ে। হাসিতে ফেটে পড়ে দুই বোন। চন্দ্রা দেখায়। ঠিক জিভে পড়ে রসফোঁটা। এবারে বাকু চেষ্টা করে। হ্যাঁ, এবারে পারে। আমাকেও বলে চন্দ্রা। আমি সাড়া দিই না, বরং অসম্মতির মুচকি হেসে হাত নেড়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকি। অথচ আলসের বিলপাড়াতে কত যে খেলেছি এ-খেলা! চন্দ্রা বুঝি রাগ করে তাতে।
বাকু করছে, ঠিক আছে। ওর দিদিবাড়ি। ওর বিয়ান। আমি কেউ নই। আর তা ছাড়া আমাকে হাভাতে ভাববে। মুখে রস লেগেলুগে চ্যাটপ্যাট করবে। কিছুক্ষণ পর চন্দ্রা বলে, ‘পুকুরপাড়ে কয়ডা ঠিলে আনতি যাই বাকুদার সাথে। তুরা খাড়া এইখানে।’ চন্দ্রার পেছনে বাধ্য ছেলের মতো বেরিয়ে যায় বাকু। যেন ‘শোলে’-র ভিরু বাসন্তীর পেছনে। কেবলই বোবা-কালার মতো দাঁড়িয়ে থাকি আলের পর। অথচ আমার মন বায়ুমণ্ডল ভেদ করে মহাকাশে পৌঁছায়।
ওরা ফেরে না। আমরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকি। কেউ কারও সঙ্গে কথা বলি না। কেন বলি না? অথচ সামান্য হাওয়াতেই দু-জনে এক হয়ে যাব! কথা কি ফুরিয়ে গেল তবে? কী আশ্চর্য, তা-ও কি সম্ভব? অবশেষে সে আমার বিরক্তি দেখে বলে, ‘ওদিকি যাবা দীপুদা?’ ব্যস, অক্সিজেন পেয়েই হাওয়ায় দুলতে থাকি আলখাল্লার মতো! কিন্তু পরক্ষণেই সে বলে, ‘আচ্ছা, তুমি ঠিলে দুডোরে পাহারা দ্যাও, আমি বরং এট্টা খোঁজান দিয়া আসি। এই যাবো আর আসপো।’ বলেই ঝড়ের বেগে উড়ে যায় সে, আর বেদনার ঝড় বয় আমার অন্তরে। কেন যে মুখ ফুটে বলতে পারছি না, ‘আমি যাব চঞ্চলা, আমি তোমার সঙ্গে যাব। উড়ব। আমারে নিয়ো চলো তুমি!’
সে-ও ফেরে না আর। আশ্চর্য! বাইসার বিলমাঠে সন্ধে নামে অদ্ভুত। চাঁদ ওঠে। আকাশের নীলাভ ভাব কাটেনি তখনও। তখনও কুয়াশা জাপটে ধরেনি এই চঞ্চলা গ্রামপৃথিবীর শরীর। চরাচর ঝিঁঝিডাকে ভরে গেছে খুব। ঘরে ফেরা পাখিরা ডাকে। শেয়ালও ডাকে। ঘিলুর অন্ধকারে তখন প্রজেক্টর রুমের প্রবল ঘড়ঘড় শব্দ। পর্দায় শীৎকার। পরদায় উল্কাপাত, জোছনাপাত। সতেরোই শ্রেষ্ঠ রমণদা, সতেরোই শ্রেষ্ঠ! অথচ দ্যাখো লিঙ্গ থেকে বীর্য নয়, কান্না ঝরছে অঝোরে! প্রবল যৌন হতাশায় মাথাটা কেবলই ঝিমঝিম করতে থাকে বিলপাড়ে। এই বুঝি পড়ে যাব গোধূলির মায়াজলে।
আরও একটু দেরি করার ফলে, উঁচু আল ধরে খুঁজতে বেরিয়ে পড়ি ওদের। সামনের চটকা গাছটা পেরোতেই দেখি বিচালির উঁচু গাদা থেকে নেমে আসছে তিনজন। গাঁদার পাশে ঘোমটা দেওয়া দুটো খেজুর গাছ দাঁড়িয়ে। কুয়াশার আড়ালে তাদের তৃপ্ত মুখ দেখা যায় স্পষ্ট।
তিন জনেরই হাতে ভাঁড় ভাঁড় রস! গাঁদার ওপাশে সার সার খেজুর গাছ। দিনের শেষ আলোচিহ্ন পড়ছে এসে বিলজলে। তাতে এখনও দু-একটা পাতিহাঁস। এ দৃশ্যে খুবই দুঃখ পাই। আমাকেও তো একবার ডাকতে পারত! ওদের আর কী বলব, যেখানে নিজের বন্ধুই এত স্বার্থপর।
চঞ্চলার মুখে জ্যোৎস্নাকণা লেগে অভ্রের মতো উজ্জ্বল! গম্ভীর মুখ তার। চঞ্চলা, তুমিও এমন? অথচ কত স্বপ্ন দেখালে কয়েক মুহূর্তে! অথচ সামান্য হাওয়া দিলেই একে-অপরের সঙ্গে লেপটে যেতাম আমরা! মনে মনে কাঁদলাম খুব। আমার মনের কথা হয়তো সে অনুভব করতে পেরেছে। তাই এগিয়ে এসে একভাঁড় খেজুর রস আমার হাতে তুলে দিয়ে মুচকি হাসি দিল দারুণ! মুহূর্তেই জোছনা ছড়িয়ে পড়ল চরাচরে।
চার
সাইকেল চালিয়ে যেভাবে আসি, ফিরে যাই সেভাবেই। সারা রাস্তা চুপচাপ থাকি। অথচ কেবলই খোঁচাতে থাকে বাকু। উত্তর দিই কিংবা দিই না। কিছুতে কিছু হবে না বুঝে গুনগুন গান ধরে সে। তারপর আবার চুপ করে যায়। আমরা ফাঁসুড়ে বটতলা দিয়েই যাই। আমরা দেবগ্রাম ফরেস্টের পাশ দিয়েও ফিরি। ভয় লাগে।
ট্রেনে উঠে মনে হয়, সাইকেল সুদ্ধ বাকুকে ফেলে দিই কামরার বাইরে!
সাইকেল কেন?
আসলে প্রবল ছেমেমানুষি চেপে বসেছে মনে। কিছু একটা না-পাওয়ার প্রতিক্রিয়া। কিন্তু কী? কাকে? চঞ্চলাকে আমি কি চেয়েছিলাম? তাহলে কেন হেলে পড়ে গেলাম না তার দিকে? গাছও তো হেলে যায় আলোর দিকে, হাওয়ার দিকে, পুকুরের দিকে। অথচ...। কিন্তু সে যদি চিৎকার করত, মেজদিবাড়ি এসে মুখ থাকত আমার? বিলপাড়ে রটে যেন দ্রুত। বড়দা-মেজদা বেলের ডাং হাতে নিয়ে ঠ্যাঙাত। হিটলার বাবা-মাও প্যাঁদাত। স্কুল, টিউশানি, খেলার মাঠ, দোলনদের বাড়ি— কোথাও মুখ থাকত না আমার। হয়তো বাকু এসেই আগে পেটাত। বন্ধু তখন হুচকো লাঠি!
ট্রেনের দরজায় বসে থাকি। ঠান্ডা হাওয়া লাগে। আজ যদিও কনকনে ভাবটা নেই আর। বসন্তের মধ্যে ডুবে যাওয়ার ইঙ্গিত তাতে স্পষ্ট। তবু চরাচরে কুয়াশা ভীষণ। স্টেশান এলে অন্ধকারে টর্চ মারেন গার্ড। দেখে নেন যাত্রীরা ঠিকঠাক উঠল কি না।
আমার পাশে এসে বসে বাকু। বড়োই তৃপ্ত দেখায় ওর মুখখানা। এই তৃপ্তিই ওকে ভীষণ অহংকারী করে তুলেছে আজ। আমার তখন বাকুকে খুন করার আকাঙ্ক্ষা আরও তৃপ্ত করে মনকে! একটা খুন, একটা আত্মহত্যা, একটা ধর্ষণ, একটা অগ্নিকাণ্ড কয়েক মুহূর্তের জন্য হলেও তো প্রবল জয় এনে দেয় মনে। মাত্র এগারো সেকেন্ডের সিদ্ধান্তে দীর্ঘ জীবন-কাহিনির পাণ্ডুলিপি পুড়ে ছাই চরাচরে। তারপর ফেরার পথ নেই আর!
আচমকা বাকুকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিই দরজার বাইরে! আহ্ কী তৃপ্তি! ঠিক ততটাই, যতটা চঞ্চলাকে পেলে তৃপ্ত হত মন! নিশ্চয়ই এতদিন ধরে এই তৃপ্তিই খুঁজছিলে তুমি, রমণদা? নিশ্চয়ই এই খুনের আগে, মৃত্যুর আগে তেমনই তৃপ্তি পেয়েছে বাকু। নিশ্চয়ই এই তৃপ্তির জন্য মরতে অনুপ্রাণিত করেছিল লিজা তার দিদিকে। জীবনের রস ও রাসে ঝুঁকি নেওয়া রমণদা সামান্য ঝুঁকি নিয়ে ট্রেনে উঠতে গিয়ে বারংবার সফল হয়েছে, কিন্তু একদিন...। ফিজা, লিজা, ভিকি সবাই আজও সেই পোড়ো হাভেলিতে। দেবগ্রাম ফরেস্টে বুঝি সেই ফিল্মি হাভেলি!
আবার সিনেমা, ভূত ও যৌনতা। সব মিলেমিশে একাকার।
ট্রেন চলছে ঝিকঝিক। মাঠের পর মাঠ পেরোচ্ছে জ্যোৎস্না-অন্ধকারে। হঠাৎ এইসময় শীতল স্পর্শ পিঠে!
‘বাকু?’
বেঁচে আছে সে? অথচ আমি যে তাকে ছুড়ে ফেলে দিলাম বাইরে! ভয়ে আমার গা-হাত-পা কাঁপছে!
ঠিক তখনই বাকু বলে ওঠে, ‘ভয় কীরে বাছা, আমি তো আছি!’ বলেই দরজার আবডালে এসে মেঝেতে লেটকে বসে একটা বিড়ি ধরায়। তৃপ্তির ধোঁয়া ছাড়ে। তার চোখদুটি সিগনাল ল্যাম্পের মতো লাল। লালের মাঝে একচোখে চন্দ্রা, আর অপর চোখে চঞ্চলা। চোখের মধ্যে সতেরোর সুতীব্র সংগম। সেই মুহূর্তে বাকুর মুখটা রমণদার মতো লাগে। ভিকির মতো লাগে। আমার চেতন-অবচেতনের অরণ্যপথ লণ্ডভণ্ড করে অন্ধকার পথে এগোতে থাকে ট্রেন। এই প্রথম বাকুর কাছে গোহারা হেরে যাই আমি। আমার শিক্ষাদীক্ষা, পৈতৃক সম্পত্তি, আমার বংশপরিচয়— সবই অর্থহীন হয়ে পড়ে বাকুর মুখের কাছে।
কেতাব-ই’র মুদ্রিত বই, ই-বই এবং ব্লগজিন বিভাগের লেখালিখির নিয়মিত খোঁজখবর পেতে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যুক্ত হোন।
এই ব্লগজিনে প্রকাশিত সমস্ত লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব।