গরুর চামড়া ছাড়াতে যাওয়া এক মুচির জীবনের নির্মম বাস্তব, সামাজিক অবহেলা আর নিভৃত পিতৃস্নেহের এক মর্মস্পর্শী কাহিনি—‘দুলালীর বাপ’। দারিদ্র্য, সমাজবিচ্ছিন্নতা আর ভালোবাসার গভীর মানবিক টানাপোড়েনে রচিত এই গল্প পাঠককে নাড়া দেবে ভিতর পর্যন্ত।
এক
প্রথমে ডান পায়ের গোড়ালির চারদিকে ঘুরিয়ে চেপে ধারালো ছুরি চালিয়ে গোল করে চামড়া কেটে নিল। তারপর পায়ের ভিতর দিক বরাবর ছুরিটা চামড়ার তলায় চেপে ঢুকিয়ে সামনের দিকে জোরে চাপ দিতে-দিতেই পায়ের চামড়া উপরের দিকে লম্বালম্বি কেটে-কেটে একেবারে তলপেটের মাঝামাঝি পর্যন্ত চলে গেল। একইভাবে বাঁ-পায়ের ভিতর দিক বরাবর চামড়া কেটে-কেটে তলপেটের ওই একই জায়গায় এসে মেলাতে হবে। তারপর সেখান থেকে মোটামুটি সরলরেখায় পেটের মাঝবরাবর ছুরি চালিয়ে চামড়া কেটে এগোতে এগোতে বুক পেরিয়ে একেবারে গলা পর্যন্ত ছুরিটা এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।
খুব দ্রুতই এসব কাজ করতে হবে। কারণ এসব কাজে বেশি দেরি করে ফেললেই বিশেষ বিপদ ঘনিয়ে আসবে। গণেশ পিছন দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে উদ্বিগ্ন চোখে সম্ভাব্য কোনো বিপদ আসছে কি না সেটা একবার ভালো করে খুঁটিয়ে দেখে নেয়। নাঃ! যতদূর নজর চলে এ তল্লাটে এখন কাউকেই দেখা যাচ্ছে না।
পিছনের ডান পায়ের চামড়া ছাড়ানো হয়ে গেছে। এবার একইভাবে বাঁ-পায়ের চামড়া ছাড়াতে হবে। তারপর পেট ও বুকের চামড়া ছাড়াতে-ছাড়াতে যে-কোনো একদিকে এগিয়ে মেরুদণ্ডের দিকে চলে যেতে হবে। তখন সামনের যে-কোনো একটা পায়ের চামড়া পুরো ছাড়িয়ে নিলেই হবে। তাহলেই মেরুদণ্ড পর্যন্ত একদিকের চামড়া পুরো ছাড়িয়ে ফেলা সম্ভব হবে।
কোনোমতে মেরুদণ্ড পর্যন্ত চামড়া ছাড়িয়ে ফেলতে পারলেই কেল্লা ফতে। তার পরে অন্য কোনো ভাগীদার এলেও আর তাকে আর এই চামড়ার ভাগ দিতে হবে না। চামড়ার তলায় সাবধানে ছুরি চালাতে-চালাতেই গণেশ আবার একবার ভালো করে চারপাশ তাকিয়ে দেখে নেয়। এবারেও আপাতনির্জন গো-ভাগাড়টার আশেপাশে বা দূরে কাউকেই দেখতে পেল না সে। সামান্য দুশ্চিন্তা কম হলেও কাজের গতি একটুও কমায় না সে। রক্ত রস লেগে পিচ্ছিল হয়ে যাওয়া তার হাত গামছায় মুছে নিয়ে মৃত গোরুটার চামড়ার ভাঁজে ছুরি চালানোর গতি সাধ্যমতো বাড়ায় গণেশ।
দুই
গণেশ দাস মুচি সম্প্রদায়ের লোক। সমাজ-জীবনের এবং দারিদ্রসীমার অনেক নিচের দিকে এদের অতি কুণ্ঠিত ও অশুচি অবস্থান। অনিশ্চিত মরশুমি দিনমজুরি এদের জীবিকা অর্জনের প্রধান উপায়। মরশুমি দিনমজুরি ছাড়া তারা গৃহস্থের ব্যবহার্য নানারকম বাঁশ ও প্রধানত বেতের জিনিস যেমন ধামা, কুলো, পালি, চুপড়ি ইত্যাদি তৈরি ও মেরামত করে থাকে।
শিক্ষিত রুচিবান সুসভ্য মানুষের সমাজে স্মরণযোগ্য কাল থেকে এরা নিতান্ত অস্পৃশ্য ঘৃণিত সম্প্রদায়ের মানুষ। ভবিষ্যতে মানব সমাজের শিক্ষা সভ্যতা যথেষ্ট এগিয়ে গেলেও এরা একইরকম অবস্থানে থেকে যাবে। সভ্য ভদ্র সমাজজীবনের বাইরে এদের অবস্থান নির্দিষ্ট বলে এদের হাতের ছোঁয়া জল-অচল বটে। তবে এদের হাতের তৈরি করা বা মেরামত করা জিনিস সব শ্রেণির সব বর্ণের গৃহস্থই সম্পূর্ণ নির্দ্বিধায় গৃহস্থালির কাজে ব্যবহার করে থাকে।
তা ছাড়া যে-কোনো বিভিন্ন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে এমনকি বিভিন্ন ছোটো-বড়ো ঠাকুরের বারোয়ারি বা গৃহস্থের পুজোর শুদ্ধাচারসম্মত আয়োজনেও এদের অপবিত্র ধিক্কৃত হাতের তৈরি বাঁশ ও বেতের জিনিস পূজোপচার সাজাতে বা বহন করতে অপরিহার্যভাবে কাজে লাগে। তবে ওই জিনিসগুলোর সৃষ্টিকারী এই মানুষরা অবশ্য ঘৃণ্য এবং নিতান্ত অসম্মানযোগ্য হয়ে আছে ওই মানুষদের সমাজে।
ওইসব জীবিকা ছাড়া আর এক আরও অনিশ্চিত জীবিকা হিসেবে সময়ান্তরে গো-ভাগাড়ে ফেলে দেওয়া মৃত গবাদি পশুর চামড়া ছাড়িয়ে বিক্রি করে কিছু উপার্জন হয় এদের। তবে এগুলো মরশুমি দিনমজুরির কাজ জোটার থেকে অনেক বেশি অনিশ্চিত। মৃত গবাদি পশুর, প্রধানত গোরুর চামড়া ছাড়িয়ে বিক্রি করতে পারলে এক হাজার থেকে দেড় হাজার টাকা পাওয়া যায়। তবে সে চামড়ার ভাগীদার জুটে গেলে মুশকিল। গৃহপালিত মোষের চামড়ার দাম অবশ্য আরও বেশি। কিন্তু বাংলার গ্রামাঞ্চলে গবাদি পশু হিসেবে মোষের তেমন চলন বা কদর নেই। যদিও যমের বাহন বলে বিদিত এই পশুটি গোরুর তুলনায় অনেক বেশি কাজের, কষ্টসহিষ্ণু এবং শান্তও বটে।
তিন
এই মৃত গবাদি পশুর চামড়া যারা ছাড়ায় তাদের মধ্যে চামড়ার দাম ভাগাভাগির একটা অলিখিত কিন্তু অবধারিত নিয়ম আছে। সে-নিয়ম ওদের সম্প্রদায়ের সবাই মান্য করে চলে। ভাগাড়ে পড়ে থাকা মৃত গোরু বা মোষের চামড়ার উপর ওদের সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা চামড়া ছাড়াবার কাজ করে তাদের সকলের অলিখিত কিন্ত ঘোষিত সমান অধিকার আছে। তবে প্রথমে কেউ এসে পড়ে মৃত পশুর যে-কোনো একপাশ থেকে মেরুদণ্ড পর্যন্ত চামড়া ছাড়িয়ে ফেলতে পারলে সেক্ষেত্রে আর সেই চামড়াটার উপর অন্যের কোনো দাবি খাটবে না।
কিন্তু গোরুর মতো বড়ো আকারের প্রাণীর মেরুদণ্ড পর্যন্ত একদিকের চামড়া ছাড়িয়ে ফেলতে পারার কাজ কঠিন ও সময়সাপেক্ষ। সেই অতি শ্রমসাধ্য কাজটা করে ফেলার আগে কেউ এসে পড়ে ভাগাড়ে থাকা সেই মৃত গোরু বা মোষ ছুঁয়ে দিলেই চামড়ার উপর তার সমান অধিকারও প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। তখন তারা দু-জনে মিলেই মেরুদণ্ড পর্যন্ত চামড়া ছাড়ানোর কাজটা যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি করতে থাকে। কারণ তার মধ্যে আবার যদি ওদের মতো অন্য কেউ এসে পড়ে ছুঁয়ে দেয়, তাহলে সেই তৃতীয়জনও সেই গোরুর চামড়াটার আরও একজন সমান ভাগীদার হয়ে দাঁড়াবে।
বরাত দোষে অনেক সময় একটা গোরুর চামড়ার চার-পাঁচজন ভাগীদার জুটে যায়। সেক্ষেত্রে সবারই প্রাপ্তি খুবই কমে যায়। এদের মধ্যে এমন কেউ-কেউ থাকে যারা গোপনে গৃহস্থের বাড়িতে বৃদ্ধ বা অসুস্থ গবাদি পশুর নিয়মিত খোঁজখবর রাখে। মারা গেল কি না খবর নেয়। মারা যাবার খবর পেলেই দ্রুত সেখানে পৌঁছে যায়। পৌঁছে গিয়ে সেই গৃহস্থকে সাহায্য করে মৃতদেহ ভাগাড়ে বয়ে নিয়ে যেতে।
অনেক গৃহস্থ আবার ভাগাড়ে নিয়ে যাবার আগে পর্যন্ত তাদের নিজস্ব সংস্কারবশত মৃত গোরুকে এদের ছুঁতে দেয় না। সেই সময় ওদের কেউ যদি ঘটনাচক্রে সেখানে উপস্থিত থাকে তবে সে অদূরে অপেক্ষা করতে থাকে। ভাগাড়ে গোরুটির মৃতদেহ পড়ামাত্রই সে ঝাঁপিয়ে পড়ে চামড়া ছাড়ানোর কাজ শুরু করে দেয়, যাতে অন্য কাউকে সেই চামড়ার ভাগ দিতে না হয়, যাতে তার অনটনে ক্লিষ্ট সংসার চলার জন্য কিছুদিনের করুণ রসদ জোগাড় হতে পারে।
চার
গণেশের বড্ড হাঁপ ধরে যাচ্ছিল। তার বয়স তিনকুড়ি পেরিয়ে গেছে। গোরুর চামড়া ছাড়ানো খুবই পরিশ্রমসাধ্য কাজ। চামড়ার সম্ভাব্য ভাগীদার এড়াতে খুব তাড়াতাড়ি ছাড়ানোর কাজটা করতে হয় বলে আরও বেশি কষ্ট হয়। আবার খুব তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে চামড়ায় ছুরির পোঁচ পড়ে যাতে চামড়ার কোথাও কেটে না-যায় সেটাও খেয়াল রাখতে হয়। কেটে যাওয়া চামড়ার ভালো দাম পাওয়া যায় না।
চামড়া ছাড়াতে-ছাড়াতে গোরুর মৃতদেহের রক্তে রসে হাতের আঙুল আর ছুরি দুই-ই পিচ্ছিল হয়ে ওঠে। সেজন্য বারবার কাজ থামিয়ে হাত ভালোভাবে মুছে নিয়ে চামড়া ছাড়াবার কাজ চালিয়ে যেতে হয়। আজ ভাগ্যবলে যদি এই চামড়ার কোনো ভাগীদার না জোটে তাহলে সংসারের অভাবের কিছু সুরাহার সঙ্গে-সঙ্গে হয়তো গণেশের বহুদিনের অন্য একটা সাধ পূর্ণ হলেও হতে পারে।
গণেশ একজন ঢাক-শিল্পী। কিন্তু প্রায় একবছর হতে চলল তার ঢাকের একদিকের চামড়ার ছাউনি ছিঁড়ে গেছে। অভাবের তাড়নায় ঢাকটা আর মেরামত করে উঠতে পারেনি। সেজন্য গত দুর্গাপুজোর মরসুমে ঢাক বাজানোর বায়না এলেও ঢাক বাজাতে যেতে পারেনি সে। ঢাক বাজিয়ে যেমন কিছু রোজগার হয় তেমনই মনের বড়ো তৃপ্তি হয় গণেশের।
ঢাক বাজানোর ক্ষেত্রে মজুরির টাকা পাওয়া ছাড়াও অন্য একটা ব্যাপার আছে গণেশের মধ্যে। ঢাক বাজাতে গিয়ে প্রায়ই সে যেন আস্তে-আস্তে তার নিজের বাজনার মধ্যে ঢুকে পড়ে। নিজেরই সৃষ্ট লয়সমৃদ্ধ দক্ষ ধ্বনি-তরঙ্গে সে এক সম্মোহিত অবগাহন করতে থাকে। তাই ঢাক বাজানোর কোনো প্রস্তাব এলে বিশেষ দরদস্তুর না করে বায়নাটা নিয়ে নেয় গণেশ। এবারে দুর্গা পুজো বা কালী পুজোর সময়ে খুব ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ঢাকের অভাবে কোনো বায়না নেওয়া আর সম্ভব হয়ে ওঠেনি।
পাঁচ
একদিকের চামড়া ছাড়িয়ে মেরুদণ্ড পর্যন্ত যখন সত্যিই পৌঁছে গেল গণেশ তখন তার বুকটা হাপরের মতো প্রচণ্ড জোরে ওঠা-নামা করছে। ছুরিটা একপাশে ফেলে রেখে মাটিতে থেবড়ে বসে পড়ে হাঁপাতে থাকে সে। বহুদিন পরে সে একটা পুরো চামড়া পেতে চলেছে। এখন কেউ এসে পড়লেও এটাতে নিয়মমাফিক আর ভাগ বসাতে পারবে না। এই গোরুর চামড়াটা এবার সম্পূর্ণ তারই। এখন সে চামড়া ছাড়ানোর কাজ বন্ধ রেখে বেশ খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিতেই পারে।
এমন সময় সে দেখতে পেল তাদের পাড়ার মাধাই দাস সেই গো-ভাগাড়ের দিকে ছুটতে-ছুটতে আসছে। একেবারে কাছাকাছি এসে মেরুদণ্ড পর্যন্ত অর্ধেকটা চামড়া ছাড়ানো হয়ে গেছে দেখে খুব হতাশ গলায় মাধাই আক্ষেপ করে ওঠে—
‘ইস্স্! মেরে দিলে গণেশদা? একা-একা পুরো চামড়াটাই আজ মেরে দিলে?’
হা-ক্লান্ত গণেশ মাধাইয়ের কথার কোনো উত্তর না দিয়ে হাঁপাতেই থাকে। দেখে-শুনে মাধাই চোখ সরু করে ফিকির খোঁজে—
‘খুব দমছুট হয়ে পড়েছ দেখছি। চামড়ার বাকিটা বরং আমিই ছাড়িয়ে দিই। শ-দুয়েক টাকা ধরে দিয়ো।’
‘শতখানেক টাকা দিতে পারি, যদি রাজি থাকিস তো লেগে যা। নাহলে আমি কাজটা করে নেব।’
‘আচ্ছা ঠিক আছে, তাই দিয়ো, তবে ভালো দাম পেলে বিশ পঞ্চাশ উপরি দিয়ো।’
গণেশ কোনো উত্তর দিল না। মাধাই নিজের ছুরি বের করে চামড়া ছাড়ানোর কাজ শুরু করে দেয়। মাধাইয়ের বয়স কম, গায়ে শক্তিও বেশি। মৃত গোরু-মোষের চামড়া সে-ই বেশি পেয়ে থাকে। আশেপাশে গ্রামের অসুস্থ বা বুড়ো গোরুর সব খবরাখবর রাখে মাধাই। নিয়মিত টহল দেয় সে সব জায়গায়। এজন্য গৃহস্থরা মাধাইকে মোটেই ভালো চোখে দেখে না। কেন-না, সে তো সব সময় কোনো-না-কোনো গোরুর মৃত্যুর প্রতীক্ষায় ঘুরে বেড়ায়।
গণেশ কখনোই তা করে না। তার স্বভাবই আলাদা। সে বেতের জিনিসপত্র তৈরি বা সারাই করার জন্য বেত আর প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। সেসবের ফাঁকে যদি কখনও মৃত গোরু চোখে পড়ে এবং সেই গোরুটা যদি বলদ বা ষাঁড় হয় একমাত্র তখনই চামড়া ছাড়ানোর জন্য সেটাতে হাত লাগায়। গাভী হলে গণেশ কখনোই তা ছোঁবে না। তার এই আচরণের এক অতি করুণ গভীর কারণ আছে।
কেতাব-ই’র ব্লগজিন বিভাগে লেখা পাঠাতে চান? মেল করুন blogzine.ketabe@gmail.com-এ। মেলের সাবজেক্ট লাইনে লিখুন ‘কেতাব-ই ব্লগজিনের জন্য লেখা’।
ছয়
গণেশের একটিই সন্তান, সেটি ছেলে। সাবালক হবার পর ছেলেটি হলদিয়ায় একটা কারখানাতে কাজ জোগাড় করেছিল। কাজের সূত্রে সেখানেই সে থেকে যায়। বাড়িতে আসত না বা মা-বাবার কোনো খোঁজখবর নিত না সে। টাকাপয়সা সাহায্য করা তো অনেক দূরের কথা। নিজের সম্প্রদায়ের মানুষদের ঘৃণা করত সে। সভ্য ভদ্র সম্প্রদায়ের একজন হয়ে ওঠার জন্য নিজের প্রকৃত পরিচয় গোপন রাখত। সেখানে কাজ করতে-করতে একসময় বাবা-মাকে না জানিয়ে একটা বিয়ে করে কর্মস্থলের কাছাকাছি জায়গায় সে সংসার পেতে ফেলেছে। এখন তো বাবা-মার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্কই সে রাখে না।
গণেশ অবশ্য প্রথম থেকেই মনে-প্রাণে একটি কন্যাসন্তান কামনা করেছিল। কিন্তু ভাগ্যের ফেরে প্রথমে জন্মাল ছেলে। ছেলে জন্মাবার পর গৃহদেবী মা মনসার কাছে মানত করেছিল গণেশ একটি কন্যাসন্তানের জন্য। সেই মানত সফল করে সাত বছর পরে জন্মেও ছিল এক কন্যা।
মহা আনন্দে কন্যার নামকরণ করেছিল গণেশ—দুলালী। সাধ্যমতো আড়ম্বরে বিধিমতে মানত চুকিয়েছিল মা মনসার। কিন্তু গভীর দুর্ভাগ্যে মাত্র আটত্রিশ দিন পরে কৌশল্যার কোল হঠাৎ খালি করে দুলালী চিরতরে চলে যায়। বছর দুই পরে সে দুঃসহ শোক কোনোমতে একটু সামলে নেবার পর গণেশ আবারও মানত করেছিল এক কন্যাসন্তানের জন্য। কিন্তু মা মনসা আর দয়া করেননি।
বেশ কয়েক বছর পরে গোপন কন্যাতৃষ্ণা মেটাতে গো-হাটা থেকে একটি মাতৃহারা বকনা বাছুর কিনে এনেছিল গণেশ। সাধ করে তারও নাম রেখেছিল দুলালী। দুলালী দেখতেও ভারি সুন্দর ছিল। তার গায়ের রং চকলেটের মতো। কপালে সাদা রঙের তিলকের মতো দাগ। সারা দেহ মসৃণ উজ্জ্বল ঠাসা লোমে ঢাকা। গণেশের নিবিড় আদর ও যত্নে দিনে দিনে চন্দ্রকলার মতো বেড়ে উঠেছিল মাতৃহারা দুলালী।
গণেশ তাকে চোখে হারাত। গণেশকে বেশিক্ষণ না দেখলে দুলালীও অস্থির হয়ে পড়ত। সকালে দুপুরে রাতে নিয়ম করে দুলালীর সারা গায়ে কতক্ষণ সস্নেহে হাত বোলাত গণেশ। তা ছাড়াও দুলালীর গলার নীচটা, ঘাড়ের দিক, দুটো কানের গোড়া, দুটো শিং-এর গোড়া আর কপালটা ভালো করে চুলকে আদর করে দিত। দুলালীকে নিয়ে গণেশের রকম-সকম দেখে তার বউ কৌশল্যা হেসে বলেছিল—
‘হ্যাঁ গো দুলালীর বাপ, দুলালী তোমার মানুষ মেয়ে হলে বিয়ে দিতে কী করে?’
‘দিতাম গো বিয়ে। মেয়ের বিয়ে দিতাম ঠিকই, তবে দেখে-শুনে খুঁজেপেতে ঘরজামাই করে তবে বিয়ে দিতাম।’
সাত
গণেশের বড়ো কপালমন্দে সেই দুলালীও খুব বেশিদিন তার কাছে থাকল না। দু-বার দুটো বাচ্ছার জন্ম দেবার পর হঠাৎ একদিন ছ্যারানি রোগ হল দুলালীর। কাছের গ্রামের হাতুড়ে ডাক্তার সময়মতোই ডাকা হয়েছিল, কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। দুলালী বাঁচল না। গণেশের বুক খালি করে দিয়ে এই দুলালীও চলে গেল। মাটিতে লুটিয়ে ছটফট করে কাঁদতে লাগল গণেশ। প্রতিবেশীরা এসে অনেক কষ্টে তার কান্না থামিয়ে তাকে শান্ত করে বলল—
‘যত কষ্টই হোক, নিয়ম মেনে এবার তো দুলালীকে গো-ভাগাড়ে নিয়ে যেতেই হবে।’
একসময় কান্না থামিয়ে শোকাহত গণেশ খানিকক্ষণ নিঝুম হয়ে বসে রইল। তারপর ভাঙা গলায় বলল—
‘হ্যাঁ, তা তো নিতেই হবে। দুলালীর সৎকার করা তো দরকার। কিন্তু আমার দুলালীকে বাঁশে ঝুলিয়ে নিয়ে যাস না।’
বাঁশের মোটা বাখারির তৈরি ধান ঝাড়াই করার একটা পাটাতন জোগাড় করে তাতে তুলে কয়েকজন মিলে কাঁধে করে দুলালীকে নিয়ে যাওয়া হল। গণেশ নিজে কাঁধ দিয়েছিল। গো-ভাগাড়ে নিয়ে যাবার পর পাড়ার একজন খানিক ইতস্তত করে বলল—
‘গণেশ নিজে মনে হয় চামড়াটা ছাড়িয়ে নিতে পারবে না। ওর হয়ে যদি অন্য কেউ...’
‘না!’—আর্তনাদ করে উঠেছিল গণেশ—‘আমার দুলালীর গায়ে কেউ হাত দিবি না। আমি ওকে মাটি দেব।’
অগত্যা অতি বিরল ব্যতিক্রমে সেই গো-ভাগাড়ের একপ্রান্তে একটা বিশাল গর্ত খুঁড়ে তাতে দুলালীকে মানুষের মতোই সমাধি দেওয়া হয়েছিল। বাড়ি ফিরে আসার পরও নাওয়া-খাওয়া ভুলে ক-দিন ধরে বুক চাপড়ে নীরব কান্না কেঁদেছিল গণেশ তার দুলালী মেয়ের জন্য।
তারপর থেকে সে যতই অভাব অনটনের দাঁতে চর্বিত হোক-না-কেন, কখনও কোনো মৃত গাভীর বা বকনার চামড়া ছাড়ানোর কাজটা গণেশ করত না। মৃত গাভী দেখলেই তার মনে পড়ে যায় দুলালীর কথা। খুব কষ্ট হতে থাকে তার। সেখান থেকে যত দ্রুত পারে সরে যায় গণেশ। দেখতে-দেখতে প্রায় চার বছর হয়ে গেল দুলালী চলে গেছে। তবুও তার সেই কষ্ট কমেনি।
আট
মাধাইয়ের অবশ্য এই ধরনের কোনো সমস্যা নেই। সে খুব বাস্তববাদী—অত্যন্ত হিসেবি লোক। তার বাড়িতেও গাইগোরু আছে। সেইসব গোরু সময়ে বা অসময়ে মারা গেলে চামড়াটা নিজের হাতে ছাড়িয়ে নিতে মাধাই কোনো অসুবিধা বোধ করে না। গোরু সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গিটাই আলাদা। কেউ দেখে গোরুর স্বাস্থ্য। কেউ দেখে গোরুর উচ্চতা—হালে জুড়লে মানাবে কি না। কেউ দেখে বয়স—অর্থাৎ আরও কত বছর গোরু কর্মক্ষম থাকবে। কেউ-কেউ গোরুর গায়ের রং ও সৌষ্ঠবও দেখে।
কিন্তু মাধাই শুধু দেখতে পায় কত বড়ো চামড়া দিয়ে গোরুটা ঢাকা। গোরুর গায়ে কোনো নতুন বা পুরোনো ক্ষত আছে কি না, অর্থাৎ গোরুটার চামড়ায় খুঁত আছে কি না। নিখুঁত চামড়া হলে কীরকম দামে বিক্রি হতে পারে তার হিসেবও কষে। বুড়ো হয়ে মরে যাওয়া গোরুর চামড়া সে ছাড়ায় বটে তবে তাতে তেমন ভালো দাম পাওয়া যায় না। কারণ বুড়ো গোরুর চামড়ায় নানারকম খুঁত থাকেই। তার চেয়ে অসুখবিসুখ হয়ে অকালে মরে যাওয়া জোয়ান গোরুর চামড়াতেই তার বেশি আগ্রহ। কারণ সেইসব চামড়ার জন্য ভালো দাম পাওয়া যায়।
গোরুর অকাল মৃত্যুতে গো-পালক গৃহস্থ শোকগ্রস্ত এবং যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কিন্তু তেমন কোনো খবরাখবর পেলে মাধাইয়ের মন গোপন খুশিতে নেচে ওঠে। চামড়াটা একা-একা ছাড়িয়ে নিয়ে পারলেই একলপ্তে অনেক টাকা হাতে আসবে। অবশ্য সে-ও বেতের আসবাব সারানোর কাজ কিছু-কিছু জানে। তবে তার হাতের কাজ তেমন ভালো নয়। গণেশের মতো দক্ষ মিস্ত্রি সে নয়।
আসলে এসব মেরারমতি কাজের অজুহাতে সে ঘোরাঘুরি করে বেড়ায় কোথায় কোন গোরু অসুস্থ হয়েছে সেই খোঁজ নেবার জন্য। অদক্ষ হাতে বেতের আসবাব তৈরি করে বা মেরামতির কাজ করে যে মজুরি পায় সে তাতে তার ঠিকমতো পোষায় না। মেরামতির কাজের ব্যাপারটা তার পছন্দেরও নয়। কম সময়ের কাজে অনেক বেশি টাকা রোজগারের পক্ষপাতী সে।
নয়
বর্ষার শেষের দিক বা শরতের প্রথমের দিকটা গ্রামের মানুষের পক্ষে বেশ অসুবিধার সময়। বিশেষ করে দরিদ্র শ্রমজীবি মানুষদের বড়ো কষ্টে কাটে এই সময়টা। তাদের ঘরে অভাব-অনটনের চূড়ান্ত অবস্থা চলে এসময়ে। প্রাকৃতিক নানা অসুবিধাও এই সময়ে খুব বেশি হয়। এসময় মাঠঘাট সব জলে টইটম্বুর হয়ে থাকে। ফলে সেসময় গবাদি পশুর চারণক্ষেত্র বলে কিছু থাকে না। বাধ্য হয়ে রাস্তার ধারে-ধারে যেখানে অল্পস্বল্প ঘাস থাকে সেখানেই খোঁটা পুঁতে তার সঙ্গে দড়ি দিয়ে দুপুর পর্যন্ত গোরু বেঁধে রাখা হয়। দুপুর হলে গোরুটাকে আবার বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। এই সময় নানা রোগব্যাধিতে গবাদি পশুর মৃত্যুর হারও বছরের অন্যান্য সময়ের তুলনায় বেড়ে যায়।
তবুও সুধন্য মণ্ডলের সাদা মস্তবড়ো সুস্থসবল জোয়ান বলদটা যখন হঠাৎ করে ধড়ফড়িয়ে মারা গেল তখন পাড়ার সবাই কম-বেশি অবাক হয়েছিল। অসুস্থ বলদটার চিকিৎসার জন্য ডাক্তার ডাকারও সময় পাওয়া গেল না। অদ্ভুতভাবে মাধাই সে-সময় কাছাকাছি কোথাও ছিল। গোরুটা মারা যাবার পরেই সে পৌঁছে গেল সেখানে। মৃত গোরুটা ভাগাড়ে নিয়ে যাবার পর সে-ই চামড়াটা ছাড়াল, একাই ছাড়িয়ে নিল।
চামড়া ছাড়ানোর কাজ শুরু হবার আগেই গৃহস্থরা সেখান থেকে চলে যায়। নিজের পোষা প্রাণীর দেহের চামড়া ছাড়ানো দেখতে কারোর ভালো লাগে না। কিন্তু সুধন্য মণ্ডল চলে গেল না। চামড়া ছাড়ানোর কাজটা শেষ হওয়া পর্যন্ত সেখানে ঠায় দাঁড়িয়ে ছিল। এবার সে এগিয়ে গিয়ে মাধাইকে বলল বলদটার পাকস্থলী চিরে দেখাতে। মাধাই সে-কাজ করতে গিয়ে গাঁইগুঁই করতে লাগল। কিন্তু সুধন্য মণ্ডল তাকে বাধ্য করল কাজটা করতে। অগত্যা মাধাই মৃত বলদটার পাকস্থলী চিরে ফেলল।
পাকস্থলী চিরে ফেলতে সেখানে দেখা গেল সবুজ কলাপাতার বেশ কিছু টুকরো আছে। অর্থাৎ গোরুটা এসব খেয়েছিল। সেই কলাপাতা খেয়ে হজম করতে পারার আগেই গোরুটার মৃত্যু ঘটেছিল। আর গোরুটা যেখানে বাঁধা ছিল তার আশপাশে কোনো কলাগাছ ছিলই না। এবার পরিষ্কার বোঝা গেল গোরুটাকে মারবার জন্য নিশ্চয়ই কেউ কলাপাতার মধ্যে বিষ দিয়ে অবোধ গোরুটাকে খাইয়ে দিয়েছিল। কিন্তু একাজ কে করতে পারল? প্রতিবেশীদের সঙ্গে সবারই কিছু-না-কিছু শত্রুতা কম বা বেশি থাকে। কিন্তু সেজন্য এতবড়ো নিষ্ঠুর অন্যায় কাজ প্রতিবেশীদের মধ্যে কেউ করবেই না।
স্বাভাবিকভাবেই সব সন্দেহ গিয়ে পড়ল মুচি সম্প্রদায়ের যে ক-জন লোক এদিকে চামড়া ছাড়াতে আসে তাদের উপরেই। প্রধানত মাধাইয়ের উপরেই সব সন্দেহ গিয়ে পড়ল। কিন্তু মাধাই কেঁদেকেটে একসা করে মা মনসার নামে তার বংশলোপের দিব্যি খেয়ে বলল এ কাজ সে কখনোই করেনি। ব্যাপারটা তখনকার মতো চাপা পড়লেও সবার মনেই গভীর সন্দেহ ও আশঙ্কা দানা বেঁধে রইল।
দশ
এই দুর্ঘটনার দিন পনেরো-কুড়ি পর। সেই গ্রামের দক্ষিণ পাড়াতে ঢোকার রাস্তা দিয়ে দুর্বল পায়ে গণেশ আসছিল। প্রায় মাসখানেক হয়ে গেল নিজের গ্রামের বাড়ি থেকে বেরোতে পারেনি সে। প্রচণ্ড জ্বরে খুব কাবু হয়ে কতদিন পড়ে ছিল বিছানায়। ওদের জ্বর-টর হলে ওষুধপত্রের তেমন ব্যাপার-স্যাপার নেই। অসুস্থ হলে ডাক্তার-বদ্যি দেখানোর বিলাসিতা গণেশদের পোষায় না। ওষুধের দোকান থেকে অল্প পয়সায় কেনা দু-চারটে অনিয়মিত ট্যাবলেটই ভরসা।
দিন তিন-চার আগে জ্বর ছেড়ে গেলেও তার শরীর বড়ো দুর্বল। আজ তার ট্যাঁকে গোরুর চামড়া ছাড়াবার ছুরিটা গোঁজা নেই। ইচ্ছা করেই ছুরিটা নেয়নি সে। গোরুর চামড়া ছাড়াবার ক্ষমতা এখন নেই তার শরীরে। তবু সে বেরিয়েছে পেটের দায়ে। ঘরে গতকাল থেকেই ঘরে চাল বাড়ন্ত। গৃহস্থের বেতের তৈরি জিনিসপত্র মেরামত করে যদি কিছু রোজগার হয় সেই আশায় শরীরে কষ্ট নিয়েও তাকে বেরোতে হয়েছে।
দক্ষিণ পাড়ায় ঢোকার মুখে ডানপাশে একটা পুকুর আছে। পুকুর পাড়ে ছোটো-বড়ো গাছের জটলার মাঝে একটুআধটু ফাঁকা জায়গাও আছে। পাড়ায় ঢোকার রাস্তা ধরে পুকুরটার পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল সে। হাঁটতে-হাঁটতে পুকুরটা প্রায় পেরিয়ে গিয়েছে সে, এমন সময় গলার মধ্যে ডেকে ওঠা একটা হালকা হাম্বা-রব ভেসে আসে পুকুরপাড় থেকে। এটা কোনো গোরুর ডাক, এক বিশেষ ধরনের চাপা ডাক। ডাকটা অনুসরণ করে তার দৃষ্টিটা ঘুরে যায় সেদিকে। তার পরেই বুকটা সজোরে ধড়াস করে ওঠে তার,
—দুলালী! দুলালী!
সেই চকলেট রঙের ঠাসা লোমে ঢাকা শরীর। সেইরকম ছোটো ছোটো ভারি সুন্দর দুটি বাঁকা শিং। কপালের মাঝখানে সেইরকম সাদা তিলক! একদৃষ্টিতে তার দিকেই তাকিয়ে আছে দুলালী! মন্ত্রমুগ্ধের মতো সেদিকে পায়ে-পায়ে এগোতে থাকে গণেশ।
দুলালী! কিন্তু কী করেই-বা তা সম্ভব? চার বছর আগেই সে তো নিজের হাতেই তার আদরের দুলালীকে গো-ভাগাড়ে মাটি দিয়েছে। অবশ্য দুলালীর দু-বারে দুটো বকনা বাছুর হয়েছিল। দুটো বকনাই তাদের মায়ের গায়ের রং অবিকল পেয়েছিল। অভাবের তাড়নায় সে-দুটো বকনা একটু বড়ো হবার পর বাধ্য হয়ে বেচে দিয়েছিল। এটা কি তাহলে তাদেরই কেউ? না কি তাদেরই কারও সন্তান এটা?
এসব ভাবতে-ভাবতে তার পা-দুটো আপনা থেকেই সচল হয়ে ওঠে। কিছুটা সম্মোহিতের মতো ধীরে-ধীরে গাইগোরুটার দিকে এগিয়ে যায় সে। এটা এই পাড়ার কারও গরু হবে। ফাঁকা জায়গা দেখে এখানটায় বেঁধে দিয়ে গেছে তারা। অল্পস্বল্প ঘাসও আছে সেখানটায়। গাইগোরুটার একেবারে কাছে গিয়ে তাকে ভালো করে দেখে সেটার ওইভাবে হামলে ওঠার কারণ বুঝতে পারে গণেশ।
শরৎকালে বড়ো বেশি ছিনেজোঁকের উপদ্রব হয়। গাইগোরুটার চারটে পায়েই খুরের মাঝখানে রক্তমাখা খাঁজে অনেকগুলো বড়ো বড়ো ছিনেজোঁক কামড়ে ধরে আছে। বারবার পাগুলো ছিটকে রক্তপানরত জোঁকগুলো ছাড়াবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে সে। মানুষ দেখে সাহায্যের আশায় হামলে উঠেছে গোরুটা। তার কষ্ট দেখে বুঝে বুকটা মুচড়ে ওঠে গণেশের।
পরম যত্নে সেই হঠাৎ দেখা ‘দুলালী’র চারটে পায়ের খুরের খাঁজ থেকে জোঁকগুলো টেনে ছাড়িয়ে ফেলে দেয় গণেশ। খুঁজে-খুঁজে ঢোলকলমি গাছের পাতা তুলে আনে। দু-হাতের তালুতে ঘষে রস করে রক্তপাত বন্ধ করার জন্য আর ব্যথা কমানোর জন্য সেই রস গভীর মমতায় সে লাগিয়ে দিতে থাকে জোঁকে কামড়ানোর আহত জায়গাগুলোতে।
সেই দুলালী বুঝতে পারে এসব যত্ন আর পরিচর্যা। আরও আদর পেতে সে এবার গণেশের কাঁধে তার মাথাটা নিজেই তুলে দেয়। দুলালী-হারা গণেশ এবার কেঁদে ফেলে। হাত দিয়ে গোরুটার গলার নীচ, কানের গোড়া সাদরে চুলকে দিতে থাকে। আরামে দুলালীর চোখ বুজে আসে আর গণেশের চোখ অরব অশ্রুতে ভেসে যেতে থাকে। ঠিক এইভাবেই তার কাছে আদর খেত তার সেই দুলালী। দু-হাতে দুলালীর গলাটা জড়িয়ে ধরে অস্পষ্ট গাঢ়স্বরে সে বলতে থাকে—দুলালী, আমার দুলালী মা!
এগারো
দুপুর গড়িয়ে গেছে। প্রায় দুটো বাজে। গোরুটাকে যে বেঁধে দিয়ে গেছিল সে এবার গোরুটাকে বাড়ি নিয়ে যাবার জন্য সেখানে চলে এসেছে। সেখানে আসার পর তার চোখে পড়ল এক অপ্রত্যাশিত দৃশ্য। গণেশ মুচি তার গাইগোরুটার গলা জড়িয়ে ধরে আছে। একবার তাকিয়ে দেখেই আতঙ্কে চিল চিৎকার করে ওঠে সে—
‘কে কোথায় আছিস ছুটে আয়! দেখে যা কী হচ্ছে এখানে! শালা গণেশ মুচি এসে আমার গোরুটাকে বিষ খাওয়াচ্ছে!’
তার সেই তীব্র চিৎকার শুনে আশপাশ থেকে কয়েকজন লোক সেখানে ছুটে আসে। গাইগোরুটার সঙ্গে ওই অবস্থায় গণেশকে দেখে প্রচণ্ড খুনে রাগ চেপে যায় সবার মাথায়। এই তো মাত্র সপ্তা দুয়েক আগেই পাশের পাড়ায় সুধন্য মণ্ডলের জোয়ান বলদটাকে এইভাবে কেউ-না-কেউ এসে বিষ খাইয়ে দিয়ে মেরে দিয়েছিল।
কে জানে এই শালা গণেশ ব্যাটাই সেদিন সেই বলদটাকে বিষ খাইয়ে মেরে দিয়েছিল কি না! এখন আবার এই পাড়ায় আজ এই গাইগোরুটাকে দুপুরের ফাঁক বুঝে চলে এসে বিষ খাইয়ে দিয়ে মারবার চেষ্টা করছে! গাইগোরুটা মরে যাবার পর এই ব্যাটা তার চামড়াটা ছাড়িয়ে বেচে দেবার মতলব করেছে!
অত্যুগ্র বন্য রাগে অন্ধ হয়ে যায় তারা। কল্পিত ভীষণ প্রতিহিংসায় একসঙ্গে সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়ে গণেশের উপর। ভালো করে কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই তাদের মিলিত নির্মম হিংস্র কিল চড় ঘুঁষির তলায় হারিয়ে যেতে থাকে দুলালীর বাপের জ্বরক্লিষ্ট দুর্বল দেহ।
কেতাব-ই’র মুদ্রিত বই,ই-বই এবং ব্লগজিন বিভাগের লেখালিখির নিয়মিত খোঁজখবর পেতে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যুক্ত হোন।
এই ব্লগজিনে প্রকাশিত সমস্ত লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব।
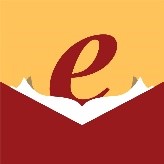

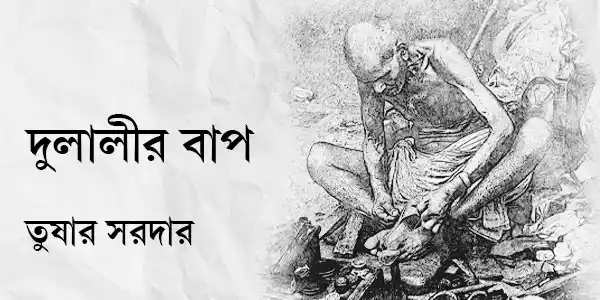




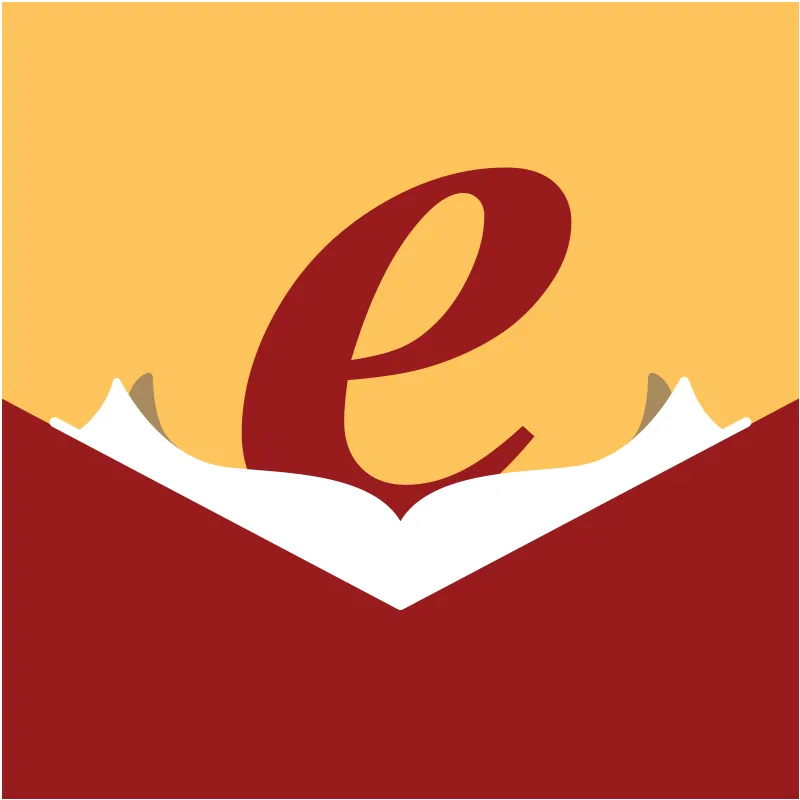
নির্বাণ বন্দ্যোপাধ্যায়
3 মাস আগেঅসাধারণ একটি গল্প।
Saswati Lahiri
3 মাস আগেএক কথায় অনবদ্য । একটি অতি বাস্তব পটভূমিকায় লেখা গল্পটি পড়তে পড়তে , লেখকের সহজ অনাড়ম্বর ভাষার দক্ষতা - শক্তি পাঠককে যেন জলস্রোতের সহজিয়া ঢঙেই টেনে নিয়ে চলে পরিণতির শেষ লাইনে। লেখকের রচনা গুণেই আপাত সাধারণ একটি বিষয়, অথচ দরিদ্র, অস্পৃশ্য গৃহস্থের সমাজ জীবন ও তার পাশাপাশি তার করুণ অপত্য যা কিনা নিজের সন্তানকে ছড়িয়ে নিরীহ প্রাণীর সঙ্গে শেষপর্যন্ত একাকার হয়ে গিয়েছে, এবং এই অপত্যের আবেগ ও হৃদয়বত্তা তাকে ( গনেশ ) এক নিষ্করুণ পরিণতিতে টেনে নিয়েছে। এখানেই গল্পটির চরম দ্বন্দিকতা গল্পটিকে সামগ্রিক ভাবে পূর্ণ করে তুলেছে। লেখককে সবিশেষ অভিনন্দন ।