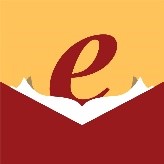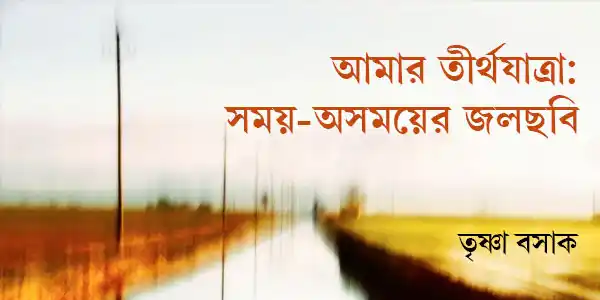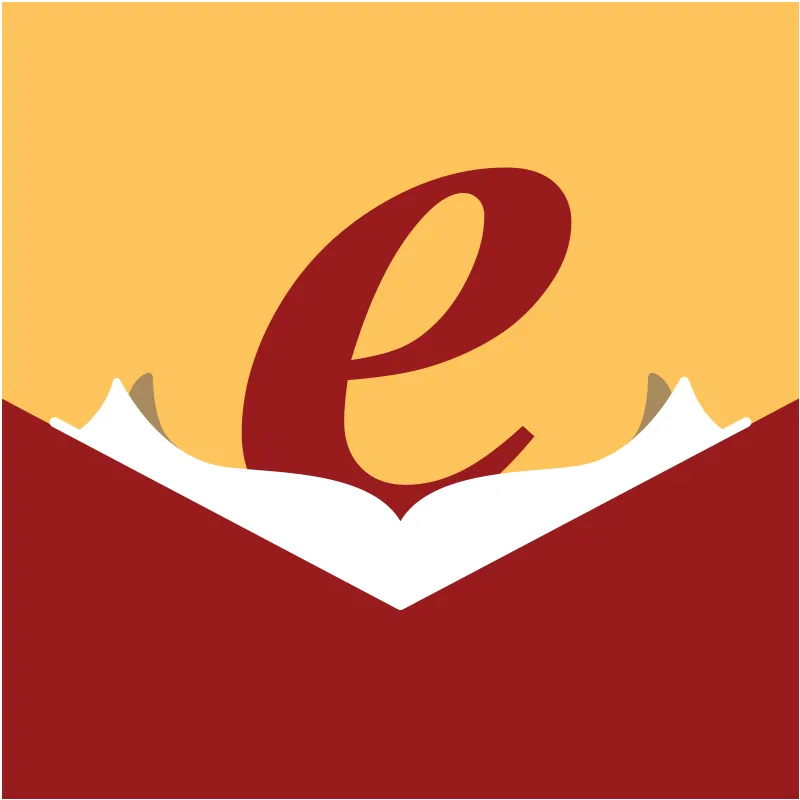রবীন্দ্রনাথ, বিভূতিভূষণ ও মণীন্দ্র গুপ্তের পাঠ-জগৎ ভেদ করে উন্মোচিত হয়েছে স্মৃতি, মহাকাব্য ও মানবজীবনের বিস্ময়।
পথের সঞ্চয়
মুম্বাই গেছি একবার। ফিরে অলসভাবে রবীন্দ্র রচনাবলীর পাতা ওলটাচ্ছিলাম। চোখ আটকে গেল এক বোম্বাই ভ্রমণে। তাঁর পর্যবেক্ষণ এক শতক পেরিয়ে আমার সঙ্গে কী অদ্ভুত মিলে গেল। আমি অবাক হয়ে ভাবলাম, এটা তো আমার ভাবনা। এই হচ্ছেন লেখক যার চিন্তার সজীবতা কালের সীমা ছাড়িয়ে যায়। বারবার তাঁর কাছে ফিরতেই হয় আমাকে। মাঝে-মাঝেই ভাবি এই শেষ, ওঁকে আমি ওভাররেট করে ফেলেছি। পর মুহূর্তেই ফিরতে হয় মাথা নিচু করে। একটু পড়া যাক বোম্বাই ঘুরে রবীন্দ্রনাথ কী লিখছেন—
“বোম্বাই শহরটার উপর একবার চোখ বুলাইয়া আসিবার জন্য কাল বিকালে বাহির হইয়াছিলাম। প্রথম ছবিটা দেখিয়াই মনে হইল, বোম্বাই শহরের একটা বিশেষ চেহারা আছে, কলিকাতার যেন কোনো চেহারা নাই, সে যেন যেমন-তেমন করিয়া জোড়াতাড়া দিয়া তৈরি হইয়াছে।
আসল কথা, সমুদ্র বোম্বাই শহরকে আকার দিয়াছে, নিজের অর্ধচন্দ্রাকৃতি বেলাভূমি দিয়া তাহাকে আঁকড়িয়া ধরিয়াছে। সমুদ্রের আকর্ষণ বোম্বাইয়ের সমস্ত রাস্তা-গলির ভিতর দিয়া কাজ করিতেছে। আমার মনে হইতেছে, যেন সমুদ্রটা একটা প্রকাণ্ড হৃৎপিণ্ড। প্রাণধারাকে বোম্বাইয়ের শিরা-উপশিরার ভিতর দিয়া টানিয়া লইতেছে এবং ভরিয়া দিতেছে। সমুদ্র চিরদিন এই শহরটিকে বৃহৎ বাহিরের দিকে মুখ করিয়া রাখিয়া দিয়াছে।
প্রকৃতির সঙ্গে কলিকাতার মিলনের একটি বন্ধন ছিল গঙ্গা। এই গঙ্গার ধারাই সুদূরের বার্তাকে সুদূর রহস্যের অভিমুখে বহিয়া লইয়া যাইবার খোলা পথ ছিল। শহরের এই একটি জানালা ছিল যেখানে মুখ বাড়াইলে বোঝা যাইত, জগৎটা এই লোকালয়ের মধ্যেই বদ্ধ নহে। কিন্তু গঙ্গার প্রাকৃতিক মহিমা আর রহিল না, তাহাকে দুই তীরে এমনি আঁটাসাঁটা পোশাক পরাইয়াছে, এবং তাহার কোমরবন্ধ এমনি কষিয়া বাঁধিয়াছে যে, গঙ্গাও লোকালয়েরই পেয়াদার মূর্তি ধরিয়াছে, গাধাবোট বোঝাই করিয়া পাটের বস্তা চালান করা ছাড়া তাহার যে আর-কোনো বড়ো কাজ ছিল তাহা আর বুঝিবার জো নাই। জাহাজের মাস্তুলের কণ্টকারণ্যে মকবাহিনীর মকরের শুঁড় কোথায় লজ্জায় লুকাইল।
সমুদ্রের বিশেষ মহিমা এই যে, মানুষের কাজ সে করিয়া দেয় কিন্তু দাসত্বের চিহ্ন সে গলায় পরে না। পাটের কারবার তাহার বিশাল বক্ষের নীলকান্ত মণিটিকে ঢাকিয়া ফেলিতে পারে না। তাই এই শহরের ধারে সমুদ্রের মূর্তিটি অক্লান্ত; যেমন এক দিকে সে মানুষের কাজকে পৃথিবীময় ছড়াইয়া দিতেছে তেমনি আর-এক দিকে সে মানুষের শ্রান্তি হরণ করিতেছে, ঘোরতর কর্মের সম্মুখেই বিরাট একটি অবকাশকে মেলিয়া রাখিয়াছে।
তাই আমার ভারি ভালো লাগিল যখন দেখিলাম শত শত নরনারী সাজসজ্জা করিয়া সমুদ্রের ধারে গিয়া বসিয়াছে। অপরাহ্ণের অবসরের সময় সমুদ্রের ডাক কেহ অমান্য করিতে পারে নাই। সমুদ্রের কোলের কাছে ইহাদের কাজ, এবং সমুদ্রের কোলের কাছে ইহাদের আনন্দ। আমাদের কলিকাতার শহরে এক ইডেন-গার্ডেন আছে, কিন্তু সে কৃপণের ঘরের মেয়ে, তাহার কণ্ঠে আহ্বান নাই। সেই রাজপুরুষের তৈরি বাগান—সেখানে কত শাসন, কত নিষেধ। কিন্তু, সমুদ্র তো কাহারও তৈরি নহে, ইহাকে তো বেড়িয়া রাখিবার জো নাই। এইজন্য সমুদ্রের ধারে বোম্বাই শহরের এমন নিত্যোৎসব। কলিকাতার কোথাও তো সেই অসংকোচ আনন্দের একটুকু স্থান নাই।
সব চেয়ে যাহা দেখিয়া হৃদয় জুড়াইয়া যায় তাহা এখানকার নরনারীর মেলা। নারীবর্জিত কলিকাতার দৈন্যটা যে কতখানি তাহা এখানে আসিলেই দেখা যায়। কলিকাতায় আমরা মানুষকে আধখানা করিয়া দেখি, এইজন্য তাহার আনন্দরূপ দেখি না। নিশ্চয়ই সেই না-দেখার একটা দণ্ড আছে।
নিশ্চয়ই তাহা মানুষের মনকে সংকীর্ণ করিতেছে; তাহার স্বাভাবিক বিকাশ হইতে বঞ্চিত করিতেছে। অপরাহ্ণে স্ত্রী পুরুষ ও শিশুরা সমুদ্রের ধারে একই আনন্দে মিলিত হইয়াছে, সত্যের এই একটি অত্যন্ত স্বাভাবিক শোভা না দেখিতে পাওয়ার মতো ভাগ্যহীনতা মানুষের পক্ষে আর-কিছুই হইতে পারে না। যে দুঃখ আমাদের অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে তাহা আমাদিগকে অচেতন করিয়া রাখে, কিন্তু তাহার ক্ষতি প্রত্যহই জমা হইতে থাকে, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। ঘরের কোণের মধ্যে আমরা নরনারী মিলিয়া থাকি, কিন্তু সে মিলন কি সম্পূর্ণ? বাহিরে মিলিবার যে উদার বিশ্ব রহিয়াছে সেখানে কি সরল আনন্দে একদিনও আমাদের পরস্পর দেখাসাক্ষাৎ হইবে না?
আমাদের গাড়ি ম্যাথেরান পাহাড়ের উপরে একটা বাগানের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ছোটো বাগানটিকে বেষ্টন করিয়া চারি দিকে বেঞ্চ্ পাতা। সেখানেও দেখি, কুলস্ত্রীরা আত্মীয়দের সঙ্গে বসিয়া বায়ুসেবন করিতেছেন। কেবল পার্সি রমণী নহে, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা-পরা মারাঠি মেয়েরাও বসিয়া আছেন—মুখে কেমন প্রশান্ত প্রসন্নতা। নিজের অস্তিত্বটা যে একটা বিষম বিপদ, সেটাকে চারি দিকের দৃষ্টি হইতে কেমন করিয়া ঠেকাইয়া রাখা যায়, এ ভাবনা লেশমাত্র তাঁহাদের মনে নাই। মনে মনে ভাবিলাম, সমস্ত দেশের মাথার উপর হইতে কত বড়ো একটা সংকোচের বোঝা নামিয়া গিয়াছে এবং তাহাতে এখানকার জীবনযাত্রা আমাদের চেয়ে কতদিকে সহজ ও সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে। পৃথিবীর মুক্ত বায়ু ও আলোকে সঞ্চরণ করিবার সহজ অধিকারটি লোপ করিয়া দিলে মানুষ নিজেই নিজের পক্ষে কিরূপ একটা অস্বাভাবিক বিঘ্ন হইয়া উঠে, তাহা আমাদের দেশের মেয়েদের সর্বদা সসংকোচ অসহায়তা দেখিলে বুঝিতে পারা যায়। রেলোয়ে স্টেশনে আমাদের মেয়েদের দেখিলে, তাহাদের প্রতি সমস্ত দেশের বহুকালের নিষ্ঠুরতা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে। ম্যাথেরানের এই বাগানে ঘুরিতে ঘুরিতে আমাদের বীডন-পার্ক্ ও গোলদিঘিকে মনে করিয়া দেখিলাম—তাহার সে কী লক্ষ্মীছাড়া কৃপণতা!...।”
(বোম্বাই শহর, পথের সঞ্চয়)
অনন্ত কাল আর অনন্ত আকাশ
একজন কোথাও যায়নি তেমন । রেলের টাইমটেবিল দেখত বসে বসে। কিংবা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে বসে পড়ত আফ্রিকার কথা, পড়ত নক্ষত্রলোক, মহাকাশের কথা। বাইরে থেকে কোন জগতবিখ্যাত বিজ্ঞানী এলে শুনতে যেত পদার্থবিদ্যার দুরূহ ও সাম্প্রতিক তত্ত্বের কথা। আমি যখন হাঁটি, আমার আগে আগে সে হেঁটে যাচ্ছে টের পাই। তার মতো আমিও জঙ্গল থেকে একটা শুকনো ডাল যোগাড় করে নিই। আমি তার পেছন পেছন হাঁটি। মা সরস্বতীকে যে জড়োয়া গয়না পরায়নি, পরিয়েছিল একটা ছোট্ট হিরের নাকছাবি, যার ছটায় বহুমূল্য জড়োয়া গয়না ম্লান হয়ে গেছে।
‘পথ আমার চলে গেল শুধুই সামনে, সামনে, দেশ ছেড়ে বিদেশের দিকে, সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্তের দিকে, জানা থেকে অজানার পানে ... মহাযুগ পার হয়ে যায়, পথ আমার তখনও ফুরোয় না, চলে চলে, এগিয়েই চলে। অনির্বাণ তার বীণা শোনে শুধু অনন্ত কাল আর অনন্ত আকাশ, চলো এগিয়ে যাই’
(বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পথের পাঁচালী)
বিভূতিভূষণ আমাকে দিয়েছেন আমার প্রতিদিনের তুচ্ছতার ওপরে এক মহাজাগতিক অস্তিত্ব, এক পথ।
উপন্যাস, ছোটোগল্প ছাড়াও বারবার পড়তে পারি তাঁর দিনলিপি, অভিযাত্রিক বা তৃণাংকুর, যে-কোনো দিন, যে-কোনো সময়ে।
কোন দুঃখ ব্যক্তিগত নয়
“গুরু গোবিন্দ মারা যান ১৭০৮ খ্রিস্টাব্দে। তার ২৩৭ বছর পরে, পাঞ্জাবে হিন্দু মুসলমান শিখদের মধ্যে আমার কয়েকটা বছর কেটেছিল। আজ মনে হয় সে বড় ভাগ্য। অল্পবয়স এবং ইতিহাসের পূর্বাপর জ্ঞান না থাকায় তখন বুঝতেই পারিনি , ঠিক যেখানটিতে চলাফেরা করছি সেইখানটিতে ভারত ইতিহাস অচিরেই পাশ ফিরে শোবে; এবং চচ্চড় করে, একখানা নতুন ম্যাপের রেখায়, ফেটে যাবে সেখানকার মাটি ও অন্তরীক্ষ। কেউ আর কোনদিন সেই ফাটলের ওপারে যেতে পারবে না।
খুব চাপা কথায় এবং তীব্র ইঙ্গিতে হঠাৎ হঠাৎ বুঝতে পারতাম শিখ ও মুসলমানদের কয়েকশো বছরের শত্রুতা। এ শত্রুতা বাঙালি হিন্দু মুসলমানের আচমকা জাগা জোলো বিদ্বেষের মতো মোটেই না; অনেক অনেক গভীর প্রবিষ্ট। তারা সুযোগ পেলেই দুই জাতি, দুই সংস্কৃতির উল্লেখ করত। অথচ আশ্চর্য, শিখ ও হিন্দুর মতো মুসলমানদেরও মুখের ভাষা ছিল চোস্ত বা ভেজাল উর্দু নয়, নিপাট আঞ্চলিক কথ্য পাঞ্জাবী। অন্যদিকে ওই তিনেরই লেখাপড়ার ভাষা উর্দু। অবাক হয়ে দেখতাম সাত্ত্বিক চেহারার হিন্দু ও শিখ বুড়োরা যাবতীয় চিঠিপত্র এবং হিসেব ফসফস করে লিখে যাচ্ছে উর্দুতে, ডান থেকে বাঁয়ে। হিন্দু ও শিখ সংস্কৃত দূরস্থান, হিন্দীও পড়তে জানে না।”
(গদ্য সংগ্রহ, মণীন্দ্র গুপ্ত)
যাঁদের বই নিয়ে বলছি, তাঁদের মধ্যে একমাত্র মণীন্দ্র গুপ্তকে আমি চাক্ষুস দেখেছি। তাঁর কাছে গেছি হয়তো সাকুল্যে চার-পাঁচ দিন। কিন্তু সে-প্রসঙ্গ আলাদা। এই একজন লেখক যিনি অনবরত আমাকে চমকে দেন, ছিয়াশি বছর বয়সেও তাঁর মস্তিষ্ক কী সজীব ছিল তা ভাবতে বিস্ময় লাগে। অক্ষয় মালবেরি তো বটেই, তাঁর কবিতা, গদ্য সংগ্রহ, শেষ জীবনে লেখা উপন্যাস, বাংলা সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ। একজন মানুষ এভাবে সব অশুভ আঁতাতের বাইরে, পীঠস্থানের বাইরে থেকে নিজেই একটা ইন্সটিটিউশন হয়ে উঠতে পারেন, ব্যক্তিগতভাবে এটা আমার কাছে একটা শিক্ষা।
নীল হিমেল রেণু কিংবা সাদা কুয়াশার জলছবি থেকে বেরিয়ে আসে একদল ছেলে-মেয়ে। তাদের ভারি ফুর্তি। তারা টুপি উড়িয়ে খেলে, দুড়দুড় করে নিচে নামে, কখনও তাদের একঝাঁক কলহাসি নুড়ির মতো বাজতে বাজতে খাদে খোঁদলে গড়িয়ে যায়। কখনও মালবেরি বৃক্ষকে ঘিরে ঘুরে চলে বালকবালিকার দল। যেন অনন্ত এক নাগরদোলা। Here we go round the Mulberry bush—গানের সুরটাও মেরি গো রাউন্ড সুরের মতো। হাত ধরাধরি করে বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে সুর করে ছড়া কাটতে কাটতে খেলতে হয় এ খেলা। অক্ষয় বট নয়, অশ্বত্থ নয়, অক্ষয় মালবেরি, কালো জামের স্বগোত্র গাছ। তাকে ঘিরে অনন্ত শৈশব, অনন্ত খেলা আর অনন্ত খাওয়া। চারদিকে যে প্রসারিত জীবন, তার কোনোটাই উপেক্ষণীয় নয় সেই খেলুড়ে বালক-বালিকার কাছে। তাদের নির্বাপণহীন ক্ষুধার হাত থেকে নিস্তার নেই কোনো কিছুরই।
একদিকে যেমন আত্মকথার একলা বালকটি বারবার উঁকি মেরে যায় তাঁর কবিতায়, অন্যদিকে বাংলা গদ্যের ইতিহাসেও অক্ষয় মালবেরি ওই একলা বালকের মতোই সঙ্গীহীন, তুলনাহীন। জীবনের এমন নির্যাস এমন মায়াময় গদ্যে আর লেখা হয়নি। নির্জন পত্রিকার বইমেলা ১৯৯৫ সংখ্যায় রূপম চট্টোপাধ্যায়কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মণীন্দ্র গুপ্ত বলছেন— “জন্ম থেকে জগতকে পাঁচ ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করেছি, আর তার বিচিত্র অর্থ মনের মধ্যে উঁকিঝুঁকি দিয়ে গেছে। ... জগতকে দেখি আমি কালস্রোতের মধ্যে-কখনো উদাসীনভাবে বহমান, কখনো অতীত বর্তমান ভবিষ্যতের আলাদা আলাদা ঘরে স্থাণু। যতদিন বাঁচি, তার সঙ্গে আমার সংযোগ, সঙ্গম, সম্পর্কের আশ্চর্য কথা বলে যাই। মনে হয়, আমার জীবনের সম্পূর্ণ অসার্থকতার মধ্যে শেষপর্যন্ত এইটুকুই সার্থকতা।” অক্ষয় মালবেরি জগতের সঙ্গে সেই সংযোগ, সংগম, সম্পর্কের আশ্চর্য কথা। আর একথা বললে অত্যুক্তি হবে না বাংলা সাহিত্যের অনেক অসার্থকতার মধ্যে অক্ষয় মালবেরি একটি অক্ষয় সার্থকতার নাম।
অক্ষয় মালবেরির ৪৫ নম্বর পাতায় একটি আশ্চর্য ছবি আছে, এই বইয়ের প্রচ্ছদ ও ভেতরের অন্যান্য ছবির মতো এটিও মণীন্দ্র গুপ্তের নিজের হাতে আঁকা। একটি বালকের হাত ধরে অরণ্যে প্রবেশ করছেন এক বৃদ্ধ। তাঁর ঊর্ধ্বাঙ্গ খালি, খাটো ধুতি, বালকটিরও অবিকল এইরকম পোশাক। মনে হয় তারা চলেছে জীবনের আদিম রহস্যের উৎস সন্ধানে। বৃদ্ধ যেন এই বালককে দিয়ে যাবেন তাঁর সারা জীবনের সোপার্জিত সম্পদ, নদী, মাটি, অরণ্য, ভেষজের যাবতীয় জ্ঞানের উত্তরাধিকার। আধুনিক বিদ্যায়তনিক পরিভাষায় একে তো ট্র্যাডিশনাল নলেজ বা টি.কিউ. বলে। সেই জ্ঞান বালক পেয়ে যাচ্ছে নিশ্বাস-প্রশ্বাস নেবার মতো সহজে। যদিও সম্পর্কে দাদু নাতি, তবু কেন জানি ক্ষীণভাবে মনে হয় এ যেন বিদুর আর যুধিষ্ঠিরের ছবি। মহাভারতের অনেক নবীন ব্যাখ্যাকার প্রায়ই যাঁদের পিতা পুত্র বলে ইঙ্গিত দেন। তো যুধিষ্ঠির বিদুরের ঔরসজাত হন বা না-ই হন, এটা তো ঠিক, বিদুরের কাছ থেকেই তিনি পেয়েছিলেন জীবনযাপনের কতগুলো আচরণসম্ভব সূত্র, জীবনের কতগুলি গূঢ় গোপন অর্থ, যেগুলি তাঁর পাবার কথা ছিল রক্তসূত্রে পিতা বা পিতামহের কাছ থেকে। ছবিটি ইশারা দেয় এই বালকটি একদিন যৌবনকে হালকাভাবে ছুঁয়ে হয়ে উঠবে পিতামহের মতোই এক চিরবৃদ্ধ, চিরবালক মুক্ত পুরুষ, যৌবনের বিধুর রাগিনীর পরিবর্তে যার কবিতায় শোনা যাবে বালকের খেলা আর বৃদ্ধের অভিজ্ঞতার সারাৎসার। বালক কেন যৌবনকে প্রায় ডিঙিয়ে গিয়েই পরিণত বয়সে পৌঁছল, তার উত্তর পাওয়া যায় তাঁরই লেখায়—
“কিশোর শরীরে তারুণ্য আর বলিষ্ঠতা যুগপৎ আসে। আমার শরীরে বলিষ্ঠতা আসছিল, কিন্তু তারুণ্য এল না। এ হল যেমন কোন বরষার দিনে ঘন মেঘ করে এল, দূর থেকে ভিজে ঠাণ্ডা বাতাস আসছে, মাঠের ঘাসে ছায়া তিন পোঁচ গাঢ় হয়ে নেমেছে, বৃষ্টি এই এসে পড়ল বলে। কিন্তু নাঃ। দু-চারবার বিদ্যুৎ চমক দিয়ে ধীরে ধীরে মেঘ কেটে গেল। মনের গুঞ্জরন, কথাবার্তা, কলস্বর যখন অন্যের কাছ থেকে প্রতিধ্বনি পায় না, তখন তারুণ্য মুখচোরার মতো সরে পড়ে। তারুণ্য একটি প্রদোষকাল। দোসরের অভাবে আমার বলিষ্টতা নিওলিথ হাতুড়ির মতো নির্মম আর ভোঁতা হয়ে উঠেছিল।”
মনে পড়ে একবার শিবরাত্রির দিন তাঁর কাছে গিয়েছিলাম। কথায় কথায় বলেছিলেন শিবের রূপকল্পটি তাঁর বড়ো পছন্দের। এখন বুঝি কেন পছন্দের। শিব হচ্ছেন সেই দেবতা যাঁর মধ্যে একাধারে বালকের নিরাসক্ত খেলা আর বৃদ্ধের প্রজ্ঞা এসে মিশেছে। উদাসীন শিব বা পিশাচ কিংবা মরুভূমিতে অপেক্ষমান সৈনিক যিনি পুরুষজন্মের ব্যথা আর সার্থকতা বোঝার পর দীর্ঘ বা ক্ষণিক কোনোরকম জীবনের জন্যেই আর কোনো খেদ অনুভব করেন না।
“ওখানে, ওই সম্পূর্ণ অবলম্বনহীনতার নৈঃশব্দ্যে
আমি শিবলিঙ্গের মতো আছি—শুধু এই কল্পনাতেই
আমি প্রলয়ের ধারণা পাই।”
এই শিবলিঙ্গের মাথার ওপর দিয়ে বয়ে যায় গঙ্গা, ভেসে যায় মাছের ঝাঁক, খেয়ার নৌকা, সাঁতারু যুবকের ছায়া। চলে যায় ইঁদুর, সাপ, শুকনো পাতা আর দিনরাত্রি। স্মৃতিকে তিনি ভষ্মের মতো ব্যবহার করেন, আর তাই অক্ষয় মালবেরি আসলে স্মৃতিকথার ছাই, যা মেখে মানুষ হয়ে উঠতে পারে না সুখী না দুখি পরম নির্লিপ্ত এক অস্তিত্ব। বারবার মনে করিয়ে দেওয়া হয়, কিছু ঘটার থেকে কিছু না-ঘটাই আমাদের জীবনের নিয়ামক। আমরা বুঝি কোনো পাপ কঠিন নয়, কোনো দুঃখ ব্যক্তিগত নয়।
“জীবন যতই মহৎ বা বিচিত্র হোক, সত্য বৃত্তান্ত না জানালে আত্মজীবনীর কোন দাম থাকে না। ... সত্য বড় ভয়ঙ্কর, সত্য বড় রহস্যময়.. আজকাল মনে হয় গুণগুলিও যেমন গুণ না, দোষগুলিও তেমন দোষ না, স্বভাবের বিচ্ছুরণ। অর্থাৎ প্রকৃতির বিচ্ছুরণ। প্রকৃতিকে এড়াবে কে! কী করে এড়াবে! এই বিশ্বই তো প্রকৃতি। ক্রমশ মনে হবে দোষগুণ কিছু না—উত্তল এবং অবতল, উচ্চ এবং অবচ, সমতল জল মাটি বাতাস আগুন এই উঠছে এই নামছে”
(আত্মজীবনী, গদ্য সংগ্রহ)
ভারতবর্ষীয় অরণ্যের মতো বিস্তীর্ণ
‘মহাভারত এক ভারতবর্ষীয় অরণ্যের মতো বিস্তীর্ণ, তাতে বৃক্ষসমূহ পরস্পরে জড়িত ও স্থূলাঙ্গ লতাগুল্মে জটিল। বহুবিচিত্র পুষ্পমঞ্জরীতে তা বর্ণিল ও সুগন্ধি, সর্বপ্রকার জীবের তা বাসস্থান’ (জার্মান পণ্ডিত জোহান জেকব মেয়ার, মহাভারতের কথা—বুদ্ধদেব বসু)
অক্ষরজ্ঞান হবার আগে থেকেই সবথেকে বেশি যে আখ্যান শুনে এসেছি, তা মহাভারতের। এখনও মনে আছে তারাভরা আকাশের নিচে বসে এক যন্ত্রণাক্লিষ্ট শিশুকে ভুলিয়ে রাখার জন্য বাবা মহাভারতের গল্প বলতেন। আর তা বলতেন বইয়ের মতো করে নয়, একেবারে নিজের ঢঙে, কখনো কখনো মহাভারতের চরিত্রদের মুখে ফিল্মি সংলাপ বসিয়ে। আর তার আর একটু পরে একটা খেলা আমাদের বিশেষ প্রিয় হয়ে ওঠে। তা হল হিন্দিতে যদি মহাভারত সিনেমা হয়, তবে কাকে কোন চরিত্র দেওয়া হবে। বাবার মুখে মহাভারতের চরিত্রদের আধুনিক সংলাপ শুনেই হয়তো এই আখ্যানের বিনির্মাণের ইচ্ছে ভেতরে ভেতরে মাথাচাড়া দেয় সেই শৈশবে। এই সময় আমি ছেলেদের মহাভারত থেকে বড়োদের মহাভারতে উত্তীর্ণ হয়েছি। মনে আছে, কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ, সম্ভবত রিফ্লেক্ট-এর, কিস্তিতে কিস্তিতে বেরোবে, তার জন্যে টাকা জমা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কেন জানি না একটি খণ্ড ছাড়া আর পাওয়া যায়নি। এই সময়েই পড়লাম গজেন্দ্রনাথ মিত্রের পাঞ্চজন্য। কৃষ্ণের দুর্জ্ঞেয় চরিত্র অনেক বছর মনকে আচ্ছন্ন করে ছিল। এত প্রভাবিত মহাভারত-নির্ভর কোনো উপন্যাস করেনি।
এরপর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পাঠের বিস্তার বেড়েছে, রুচিও বদলেছে। ইরাবতী কার্ভের যুগান্ত, বুদ্ধদেব বসুর মহাভারতের কথা, প্রতিভা বসুর মহাভারতের মহারণ্যে, আরও কত পাঠ। কতরকমভাবে ভাবা যায় এই মহাকাব্যকে।
মহাভারত নিছক কোনো গ্রন্থ নয়, সদা পরিবর্তনশীল প্রকৃতির বিচ্ছুরণ, ওঠা আর নামা, যাকে ঘিরে প্রাণের নৃত্য চলে, চলতেই থাকে। সেই গুজরাটি গল্পের মতো। যে লাইব্রেরিতে রোজ একটিই বই পড়তে যেত আর গিয়ে দেখত, বইটা রোজ একটু একটু করে বদলে যাচ্ছে। এঁরা সেই হাইপার টেক্সট দিয়ে গেছেন। সাধন চট্টোপাধ্যায় এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন কাহিনি নয়, টেক্সট লেখো। টেক্সট থেকে যায়।
কেতাব-ই’র ব্লগজিন বিভাগে লেখা পাঠাতে চান? মেল করুন blogzine.ketabe@gmail.com-এ। মেলের সাবজেক্ট লাইনে লিখুন ‘কেতাব-ই ব্লগজিনের জন্য লেখা’।
তীর্থরেণু
খালের পেঁকে ঠেলে যখন নাও।
পিছন দিকে যে চিন থাকে
তাতেই মেলে ভাও।
যখন গহিন জলে পাল তুইল্যা নাও যায়
পথের যে চিন কি বা মিলায়
কেমনে বা ভাও পায়।
(মহাসাধক গঙ্গারাম)
যখন নাও থাকে খালের পাঁকে আটকে, তখন তো পেছনের পাঁকে তার চিহ্ন থাকে, কিন্তু যখন নৌকো গহীন জলে পাল তুলে চলে তখন জলে কি আর পথের চিহ্ন পাওয়া যায়, জলে হারিয়ে যায় পথের চিহ্ন।
এই কথা বলা যায় আমাদের অনেক সাধক কবিদের সম্পর্কে। তাঁদের জন্ম কোথায় কবে, বাবা মা কারা, এসব তথ্য আমরা কিছুই পাই না, শুধু তাঁদের কবিতা গান, কালের করাল গ্রাসকে কাঁচকলা দেখিয়ে বেঁচে থাকে। সত্যি বলতে কি এগুলি তাঁদের চিহ্ন। বড়ো বড়ো খুনি ডাকাতদের ইতিহাস থাকে, কিন্তু সাধকদের ইতিহাস প্রায় থাকেই না।
যেমন ভক্ত রবিদাস, বা রুইদাস। তিনি জাতে ছিলেন মুচি। রাস্তা ঝাঁট দেওয়াও তাঁর কাজের মধ্যে পড়ে। এমন তথাকথিত হীন জন্ম সেইসময়ের অনেকেরই। মধ্যযুগে ভারতীয় সাধনার মন্দিরে তাঁরাই ছিলেন প্রধান বিগ্রহ। সারাদিনের কায়িক শ্রমের অভিজ্ঞতা থেকে তাঁরা এমন সব সৃষ্টি করে গেছেন। অতুলনীয় তাঁদের আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য। এই ধন পাবার জন্যে মহাগুরু রামানন্দ তাঁর জাতকুল বিসর্জন দিলেন। সেই রামানন্দের শিষ্য কবীর, রবিদাসও। সেই হিসেবে রবিদাস হলেন কবীরের গুরুভাই।
সেই সময়ের অনেকেরই এমন ‘হীন’ জন্ম। কবীর জোলা, রবিদাস মুচি, সদনা কসাই, ধনা জাঠ, সেনা নাপিত, নাভা ডোম, দাদূ ধুনকর, রজ্জব- এঁরা সবাই মহাসাধক।
কবীরকে একবার একজন জিজ্ঞেস করেছিলেন ‘ভগবানের কাছে পৌঁছবার পথ কি? ‘কবীর সপাট উত্তর দিয়েছিলেন, ‘পথ কথাতেই তো দূরত্বকে মেনে নেওয়া হয়। তাঁর আর আমার মধ্যে দূরত্ব কি সম্ভব? তিনি প্রাণ আমি প্রাণী। দূরত্ব থাকে কেমন করে?’
দূর অহৈ তো পন্থ ভি আহি
দূর নহী তো পন্থ ভি নাহি
দূর থাকলেই তবে থাকে পথ। দূর যদি নেই তবে পথও নেই। ‘স্তনের দুধ তো বাছুর অশুচি করল। ভ্রমর ফুলকে মাছ জলকে অপবিত্র করল। তাহলে গোবিন্দের পূজার ফুল কোথায় পাব? আর ফুল অনুপম হয় কি? মলয় চন্দন বৃক্ষ জড়িয়ে থাকে সাপ, বিষ আর অমৃত বাস করে একসঙ্গে’
তাই চলো চলো রাহি, আরও চলো, দেখো কোথায় প্রভুর প্রেমের সীমা। সীমা তো নেই। কৃপার হিসাব করতে গেলে অনন্তকাল যে চলে যায়।
অতএব চলো রাহি চলো। সামনে জীবনের পথ পড়ে, এগিয়ে চলো। শুধু যে মানুষ পশু প্রাণী হাঁটছে তা তো নয়, সারা বিশ্বই নৃত্যপর ছন্দে চলেছে, কোটি কোটি সূর্য তারা আরতি করছে সেই পরমেশ্বরের। তাঁর সঙ্গে মেলবার জন্যেই তো এই আকুল পথ চলা।
কিন্তু চলব যে, পথে তো কত বাধা, যদি পড়ে যাই, যদি ব্যথা লাগে, তবে?
আরে অবোধ শোন
মার্গ চলতা কয় গিরে তাকো লগই ন দোষ
বিপদ ভয় যো বইঠা রহে ইয়হি মহা আফসোস
পথ চলতে গিয়ে কেউ যদি পড়েও যায়, তবু তাতে কোনো দোষ লাগে না। পাছে পড়ে যেতে হয়, এই বিপদের আশংকাতেই যারা বসে থাকে, এটাই দারুণ আপশোশের কথা।
‘না মৈ দেবল না মৈ মসজিদ
না কাবে কৈলাস মেঁ
না তৌ কৌন ক্রিয়া কর্ম মেঁ
নহি যোগ বৈরাগ মে
খজি হয় তো তুরতে মিলিহৌ
পল ভ্যকি তালাস মেঁ
কহৈ কবীর সুন ভাই সাধো
সব শ্বাসো কি শ্বাস মে’
আর কুম্ভনদাস? তাঁর গল্প শুনলে তো একজন কবিকে কীভাবে প্রতিষ্ঠানকে পাশ কাটিয়ে বেঁচে থাকতে হয়, তা শেখা যায়। শোনা যাক মানসিংহের মুখ থেকেই—
“জাঁহাপনা, রণক্লান্ত হয়ে আমি আগ্রার দিকে ফিরছিলাম। ভাবলাম এতদিন পরে এ পথে ফিরছি। একবার মথুরা বৃন্দাবন হয়ে যাই। তো থামলাম মথুরায়। বিশ্রামঘাটে স্নান করে কেশব রায় দর্শন করলাম। তারপর বৃন্দাবনের দিকে যাত্রা শুরু করলাম। বৃন্দাবনের মহন্তরা যখন শুনলেন আমি আসছি, তখন তাঁরা নিজেদের ঠাকুরকে অনেক হিরে জহরতে সাজালেন। একে প্রচণ্ড গরম, তার ওপর মন্দিরে মন্দিরে এত রত্ন মণি মাণিক্যের প্রদর্শনী, আমার আরও গরম লাগছিল। আমি মন্দিরের পর মন্দির খাড়া হয়ে ঠাকুর দর্শন করলাম, প্রণত হতে পারলাম না। নিজের শিবিরে ফিরে এসে ভাবলাম এখান থেকে যেতে পারলে বাঁচি।
আবার চলা শুরু হল। দিনটা ছিল প্রচণ্ড গরম। বেলা তখন তিন প্রহর। এসে পৌঁছলাম গোবর্ধন গ্রামে। মানসী গঙ্গার ওপর শিবির ফেলতে বলে গেলাম হরদেবজির মন্দিরে। সেখানেও দেখি বৃন্দাবনের মহন্তদের মতোই আড়ম্বর। সেখানেও কোনোমতে একটা প্রণাম ঠুকে বেরিয়ে পড়লাম। কে যেন বলল, ‘মহারাজ গোবর্ধননাথজি দর্শন করবেন না? সে অতি মনোহর মূর্তি’
আমি ভাবলাম বৃন্দাবনের রাজা গোবর্ধননাথ, তাঁকে দর্শন না করে যাব কেমন করে? তাই এলাম গোপালপুর গ্রামে। সেখানে তখন ঠাকুরের ভোগ হচ্ছিল। মন্দিরের দরজা বন্ধ। গরমে ক্লান্তিতে তখন আমার বিপর্যস্ত অবস্থা। এমন সময় মন্দিরের দরজা খুলে গেল। আমি ভেতরে প্রবেশ করতেই আমার সব ক্লান্তি দূর হয়ে গেল। গোলাপজলের ধারায় ঘরখানি বড়ো শীতল ছিল। ঠাকুরের শ্রীমুখ দেখে শান্তি পেলাম। তখন মৃদঙ্গ বাদ্য সহযোগে কীর্তন চলছিল। কুম্ভন দাসজি সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গাইছিলেন
‘রূপ দেখ নইনা পল লাগই নহি
গোবর্ধনকে অঙ্গ অঙ্গ প্রতি
নিরখি নইন মন রহত তহি
রূপ দেখে চোখের পলক পড়ে না, তাঁর প্রতি অঙ্গের যেখানেই চোখ পড়ে ইচ্ছে করে চেয়ে থাকি।
এরপর তিনি গাইলেন ‘আবত মোহন মন জু হরো হৈয়’ এসেই মোহন আমার হৃদয় হরণ করেছে।
আহা কী শুনলাম। দর্শন শেষে শিবিরে তো ফিরে গেলাম। সবাইকে জিজ্ঞেস করলাম, মন্দিরে যিনি গান গাইছিলেন তাঁর নাম কী?
—উনি তো ব্রজবাসী। ওঁর নাম কুম্ভন দাস। শোনেননি একবার ওঁকে আকবর বাদশা ডেকেছিলেন?
তখন জাঁহাপনা মনে পড়ল, আমি সেসময় ছিলাম না। তবে কানে এসেছিল। আমার বড়ো সাধ হল আর একবার এঁর কাছে যাই।
পায়ে হেঁটে গেলাম পরাসোলি গ্রামে। তখন কুম্ভন দাস স্নান করে উঠে প্রাণের ঠাকুরের সঙ্গে কথা বলেছেন।”
“আসব জাহাঁপনা?”
মানসিং-এর কথায় বাধা পড়ল। তানসেন এসেছেন। এই বারিশখানায় এমন একান্ত কয়েকজনই আসতে পারেন।
“এসো তানসেন, বোসো, মানসিং-এর কহানিটা শুনে নাও। তোমার ভালো লাগবে।”
তানসেনের মুখে অন্যদিনের মতো প্রশান্তি নেই, সেটা আকবর লক্ষ করেন। কিন্তু মানসিং-এর কথা শেষ না হলে তিনি তানসেনকে কিছু জিজ্ঞেস করবেন না।
মানসিং আবার শুরু করেন—
“কুম্ভন দাসের সঙ্গে তাঁর এক ভাইঝি বসেছিল। আমাকে ঢুকতে দেখে সে কুম্ভন দাসের কানে কানে বলল, মহারাজ এসেছেন। শুনতে পেলাম কুম্ভন দাস তাকে বলছে্ ‘তাই তো তাই তো। কী করি এখন, ঠাকুর সরে গেলেন যে। আগে তাঁর সঙ্গে কথাটা সেরেনি, তুই ততক্ষণ মহারাজের কাছে থাক।’ মেয়েটি এসে আমাকে বসতে দিল। তারপর কুম্ভন দাস তাকে ডেকে বললেন ‘এবার আমার আরসি এনে দে, কপালে তিলক কেটে নি। মহারাজ বলে কথা’
মেয়েটি বলল, ‘আরসি তো বাছুরে খেয়ে গেছে’
আমি অবাক হয়ে মেয়েটিকে শুধোলাম, আরশি আবার বাছুরে খায় কী করে?
মেয়েটি কোনো উত্তর না দিয়ে একটা কাঠের বাটিতে জল এনে কুম্ভন দাসের সামনে ধরল। তিনি জলে মুখ দেখে কপালে তিলক কেটে নিলেন। তখন বুঝলাম এই জলই খেয়ে গেছিল বাছুর। এই জলই কুম্ভন দাসের আরশি। তখন জাঁহাপনা আমার সোনার আরশি কত দিতে চেষ্টা করলাম তাঁকে। তিনি কিছুতেই নিলেন না। বললেন, মহারাজ আমাকে কেন বিপদে ফেলতে চাও? চোর ডাকাতে ও আরশি লুটে নেবে।
তারপর জমি জাগির ধনরত্ন কত কিছুই দেবার বাসনা জানালাম। তিনি সব কিছুতেই না করলেন। খুব মন খারাপ হয়ে গেল। আপনি কিছু অন্তত নিন। তখন কী বললেন জানেন জাঁহাপনা? বললেন, ‘আপনি মহারাজ একটা জিনিস দিন আমাকে। সেটা হল আমার মতো দীন দরিদ্রের কুটিরে আপনি আর কখনও আসবেন না বলুন। আমার সামান্য এইটুকু হৃদয় সামান্য ভাবভক্তি। ঠাকুরের সেবাতেই কুলোয় না। আপনার মতো রাজা মহারাজা এলে যে আমি একেবারে নিরুপায় হয়ে পড়ি। আপনি এইটুকু অনুগ্রহ করুন’
মাথা নিচু করে চলে এলাম জাঁহাপনা।
সেদিন থেকে মাঝে-মাঝেই ভাবি, কী বিচিত্র এই দেশ হিন্দুস্থান, এখানকার দীন দরিদ্রের মধ্যেও কত তাগদ যে কুটিরের দরজা থেকে রাজাকেও মাথা নিচু করে ফিরিয়ে দিতে পারে, প্রত্যাখ্যান করতে পারে রাজার দেওয়া উপহার।”
তানসেন বলে ওঠেন, “এই হিন্দুস্থান, যেখানে রাজার প্রাসাদ, রাজসুখ ছেড়ে রানি নেমে আসেন পথের ধুলোয়। অনেক মনের শক্তি লাগে। তাই তো বাইরে থেকে এসে হিন্দুস্থানকে জয় করা যায় না। নিজের হয়ে যেতে হয়।”
আমি এই ভারতবর্ষের খোঁজ পেয়েছি ক্ষিতিমোহন সেনের সাধক ও সাধনায়। এই আমার তীর্থযাত্রা।
কেতাব-ই’র মুদ্রিত বই,ই-বই এবং ব্লগজিন বিভাগের লেখালিখির নিয়মিত খোঁজখবর পেতে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যুক্ত হোন।
এই ব্লগজিনে প্রকাশিত সমস্ত লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব।