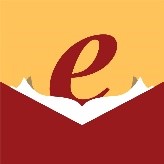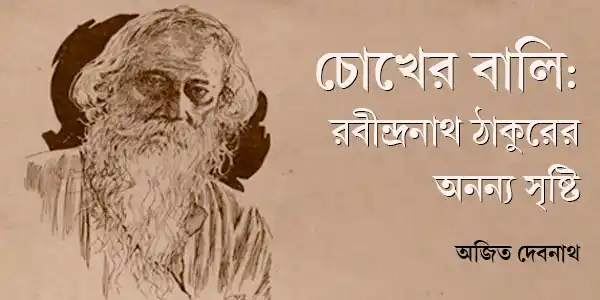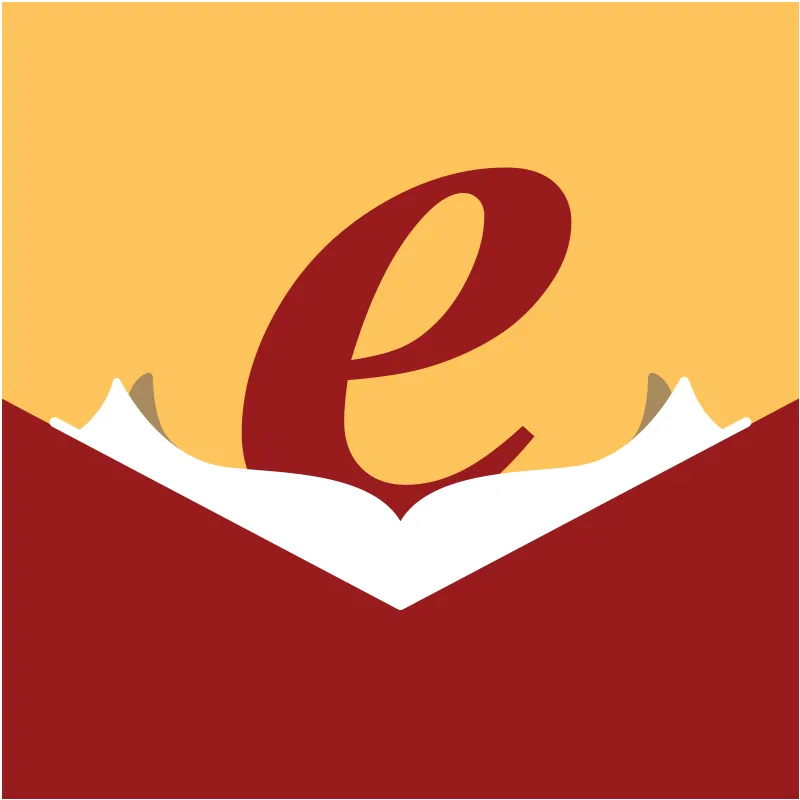রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চোখের বালি—শুধু প্রেমের উপন্যাস নয়, মানবমন, সমাজ ও অস্তিত্বসংকটের এক গভীর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। বিনোদিনী, মহেন্দ্র, আশা ও বিহারীর সম্পর্কের টানাপোড়েনে উদ্ভাসিত হয় ভালোবাসা, অহং, কর্তব্য ও আত্মমর্যাদার শাশ্বত দ্বন্দ্ব। বাংলা সাহিত্যের প্রথম আধুনিকতার দীপ্ত প্রতীক এটি।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা সাহিত্যে যে নতুন ধারা সূচনা করেছিলেন, তার এক উজ্জ্বল নিদর্শন চোখের বালি (১৯০৩)। উনিশ শতকের শেষে ইউরোপে যেমন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও সামাজিক পরিবর্তনের স্রোত বইছিল, তেমনি ভারতে সমাজ–সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটছিল। এই পরিবর্তনের মধ্যে মানুষের অস্তিত্ব, সম্পর্ক, প্রেম, কর্তব্য ও স্বপ্নের সংঘাত বাংলা সাহিত্যে প্রথম পূর্ণাঙ্গ শিল্পরূপ লাভ করে চোখের বালি উপন্যাসে।
রবীন্দ্রনাথ প্রথমে ইতিহাস–নির্ভর রচনা দিয়ে উপন্যাস জগতে প্রবেশ করেছিলেন, যেমন ভানুসিংহের পদাবলীর কাব্যমুখর আবহ বা রাজর্ষির ঐতিহাসিক কাহিনি। কিন্তু ইতিহাস তাঁর সৃজনতৃষ্ণা মেটাতে পারেনি। তিনি উপলব্ধি করলেন বাস্তব জীবনের ছোটোখাটো টানাপোড়েন, প্রেম-অপ্রেম, দুঃখ-বেদনার গল্পেই লুকিয়ে আছে সাহিত্যের প্রকৃত সত্য। সেই বাস্তব জীবনের মনস্তাত্ত্বিক গভীরতা নিয়েই গড়ে ওঠে চোখের বালি।
প্রথমে এটি ছিল একটি ছোটোগল্প, নাম বিনোদিনী (১৮৮০)। পরে সেই ছোটোগল্প পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসে চোখের বালি হিসেবে রূপান্তরিত হয়। রবীন্দ্রনাথ এখানে চরিত্রগুলোকে কেবল বাহ্যিক ঘটনাপ্রবাহে নয়, অন্তর্জগতে, মনের লুকোনো কুঠুরিতেও প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। জীবনানন্দ দাশ বলেছিলেন, “সাহিত্য মানুষের মনের গোপন ইতিহাস।” রবীন্দ্রনাথের এই উপন্যাস তারই নিদর্শন।
উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র বিনোদিনী। সুন্দরী, শিক্ষিতা, রুচিশীল এই যুবতী জীবনের প্রারম্ভেই বঞ্চনার শিকার। মহেন্দ্র প্রথমে তার সঙ্গে বিবাহে সম্মত হলেও শেষ মুহূর্তে সে পিছিয়ে যায়। ফলে বিনোদিনী বাধ্য হয় অসুস্থ ও মৃত্যুপথযাত্রী এক বৃদ্ধকে বিয়ে করতে। অর্থাৎ সামাজিক যন্ত্রণা ও অল্প বয়সে বৈধব্য তার নিয়তি হয়। কাজী নজরুল ইসলাম নারীর বেদনা সম্পর্কে লিখেছিলেন, “নারী আজ দাসী, দাসীর সমান, এ লজ্জা কি আমাদের নয়?” বিনোদিনীর চরিত্রে সেই সামাজিক অপমানেরই প্রতিফলন ঘটে।
তবে বিনোদিনী কেবল করুণার পাত্রী নয়, সে যেন এক অগ্নিশিখা। সে বিদ্রোহ করে, প্রতিশোধ নেয়, আবার ভালোবাসেও। সে বিদ্রোহী, সে প্রলুব্ধকারিণী, সে প্রেমিকা। মহেন্দ্রকে সে প্রশ্ন করে, “তুমি কি ভেবেছিলে আমি দুঃখিনী বিধবা, আমার কোনো অভিমান নেই, কোনো অধিকার নেই?” বিনোদিনী নিজের দুঃখকে প্রতিশোধে পরিণত করেছে, তবে তার প্রেমও সত্য। বিহারীর প্রতি তার কোমল অনুরাগের সঙ্গে মিশেছে আত্মমর্যাদার দীপ্তি। বিহারীর প্রতি তার আকর্ষণ যেমন সত্য, তেমনি মহেন্দ্রকে আকর্ষণ করার খেলা যেন তার অস্তিত্বের প্রতিশোধস্পৃহা। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে দেখা যায়—বিনোদিনী নিজের দুঃখ, হীনমন্যতা ও অভিমানকে নিয়েই খেলা করতে ভালোবাসে। রবীন্দ্রনাথ তার মুখ দিয়ে নিজের অনুভূতির কথা প্রকাশ করেছিলেন, “নিজের মনও কি সব জানে?”
মহেন্দ্র চরিত্রটি রবীন্দ্রনাথ গড়েছেন আত্মপ্রেম ও বিলাসের ছাঁচে। শৈশব থেকে মা ও কাকিমার অতিরিক্ত আদরে মানুষ হয়ে তার ভেতরে দায়িত্ববোধ বা মানবিক গুণের বিকাশ হয়নি। একসময় সে মায়ের ভালোবাসার ঘাটতি পূরণ করতে বিয়ে করতে আগ্রহী ছিল না, আবার বন্ধুর প্রেয়সী আশাকে হঠাৎ বিয়ে করে। আশার সঙ্গে উদ্দাম প্রণয়লীলায় মগ্ন হয়ে সংসার, মা সব ভুলে যায়। একসময় স্ত্রীকে উপেক্ষা করে বিনোদিনীর প্রতিও আকৃষ্ট হয়। যখন বোঝে বিনোদিনীও তাকে তেমন গুরুত্ব দেয় না, তখন সে মর্মাহত হয়। মহেন্দ্র যেন নিজেকেই ভালোবাসে, “আমার চিত্ত আমারই।” অতুলনন্দ দাস মন্তব্য করেছিলেন, “মহেন্দ্রর চরিত্র আত্মপ্রেমের এক অতি সূক্ষ্ম ছায়া, যে প্রেম শেষপর্যন্ত অন্যের জীবনকে ভস্ম করে।” আশার কাছে যেমন সে এক অসহ্য স্বামী, বিনোদিনীর কাছে তেমনি এক অপূর্ণ পুরুষ।
কেতাব-ই’র ব্লগজিন বিভাগে লেখা পাঠাতে চান? মেল করুন blogzine.ketabe@gmail.com-এ। মেলের সাবজেক্ট লাইনে লিখুন ‘কেতাব-ই ব্লগজিনের জন্য লেখা’।
বিনোদিনীর জীবনে বিহারী এক অনন্য চরিত্র। প্রথমে বিনোদিনী তাকে সাধারণ মনে করলেও ক্রমে আবিষ্কার করে তার মনের গভীরতা। রবীন্দ্রনাথ তার চরিত্র নির্মাণ করেছেন এক মনস্তাত্ত্বিক সূক্ষ্ম সূত্রে—বিনোদিনীর আবেগেই তার আত্মপ্রকাশ। বিহারীর অন্তরে শুধু প্রেম নয়, বরং তার পৌরুষের জাগরণ ঘটেছে বিনোদিনীর সংস্পর্শে। বিহারী প্রেমিক যেমন, তেমনি মানবিক দায়িত্ববান পুরুষও বটে। তার ভেতরে পৌরুষের জাগরণ ঘটেছে বিনোদিনীর সংস্পর্শে। তাই বিহারী বলতে পেরেছে, “তুমি আমাকে যেমন করে চিনিয়েছ, আমি তেমন করে নিজেকে কখনও চিনিনি।” রবীন্দ্রনাথ যেন এখানে বলতে চেয়েছেন, “প্রেম মানুষকে শুধু পীড়া দেয় না, তাকে পূর্ণ করে তোলে।” আশাকে যেমন তিনি শ্রদ্ধা করেন, বিনোদিনীকেও তিনি আঘাত দিতে চান না। তার চরিত্রে ফুটে ওঠে রবীন্দ্রনাথের সেই মানবতাবোধ, যা প্রেমকে কেবল ভোগ নয়, পূর্ণতার পথ হিসেবে বিবেচিত হয়।
রাজলক্ষ্মী চরিত্রটিও অতি সূক্ষ্ম এক মনস্তাত্ত্বিক সূত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত। মহেন্দ্র সম্পর্কে রাজলক্ষ্মীর স্নেহের মনোভাব বাড়াবাড়ি মনে হলেও মনস্তাত্ত্বিক বিচারে তার মনোভাব আত্মপ্রতিষ্ঠার নামান্তরও বটে। মহেন্দ্রর ভেতর দিয়ে রাজলক্ষ্মী রসিয়ে রসিয়ে নিজের প্রাধান্য উপভোগ করেছে। মায়ের প্রাধান্য ক্ষুণ্ন হবে মনে করে রাজলক্ষ্মীকে বিয়ে করে যেমন খুশি হয়েছে, তেমনি তার অমতে বিয়ের পর বউ নিয়ে মাতামাতি রাজলক্ষ্মীর ক্ষোভে পরিণত হয়। তখনই সে বিনোদিনীকে দেখে বলে ওঠে, ‘মা, তুই আমার ঘরের বউ হলিনে কেন, তা হইলে তোকে বুকের মধ্যে করিয়া রাখতাম।’ রাজলক্ষ্মী তার স্বরূপ বুঝতে না পারলেও বিনোদিনী ঠিকই বুঝেছিল। তাই সে প্রত্যুত্তরে বলে, “সে কথা ঠিক পিসিমা, কেহ কাহাকেও জানে না। নিজের মনও কি সব জানে। তুমি কি কখনও তোমার বউয়ের উপর দ্বেষ করিয়া এই মায়াবিনীকে দিয়ে তোমার ছেলের মন ভুলাইতে চাও নাই? একবার ঠাওর করিয়া দেখো দেখি।” এখানেই রাজলক্ষ্মী চরিত্রের পূর্ণ রূপটি ধরা পড়ে।
আশা চরিত্রটি ছোটো মনে হলেও তার বিবর্তন কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। প্রথম দিকে অবলা, সরলা, অপরিণত বুদ্ধির বালিকা আশা শেষের দিকে কিছুটা আত্মবোধসম্পন্ন হয়। সময়ের গতিপথে আশা চরিত্রের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। তা মহেন্দ্রও লক্ষ করে। শেষপর্যন্ত তার কাছে আশার যে মূর্তি ধরা দেয়, এ যেন মহেন্দ্রর কাছে নতুন। এই আশার মধ্যে কোনো সংকোচ নেই, দীনতা নেই; এই আশা নিজের অধিকারের মধ্যে অধিষ্ঠিত। যেটুকুর জন্য সে মহেন্দ্রর কাছে ভিক্ষাপ্রার্থী নয়। শামসুর রাহমান যথার্থভাবে বলেছেন, “নারী আজ নিজের অধিকারে দাঁড়িয়েছে, কারও দয়া ভিক্ষা নয়।” আশার পরিণতি তেমনই এক পরিবর্তনের প্রতীক।
উপন্যাসে অন্নপূর্ণার ভূমিকা নগণ্য হলেও, অবান্তর বলা যায় না। সে বিহারী ও আশার, বিশেষ করে আশার আত্মাধিক শক্তির প্রতীক। সে চাইলে মহেন্দ্রকে ফেরাতে পারত, আবার আশাকেও শিক্ষিত করতে পারত। কিন্তু অশান্তি এড়াতে সে অভিমানবশত কাশী গমন করে। এই চরিত্রটির মধ্যে সূক্ষ্ম অভিমানের রেশ ও সামান্য একটু জটিলতার সঞ্চার করেন লেখক। কাহিনির ওপর ভর করে রবীন্দ্রনাথ চরিত্রের অন্তর্জগতের জটিল রহস্য উদ্ঘাটনে উৎসাহী হন। বিধবা তরুণীর মনোবেদনা ও সামাজিক অবস্থান মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।
চোখের বালি শুধুমাত্র একরৈখিক প্রণয়গাথা নয়। তা যেন মানবমনস্তত্ত্ব, সমাজ-বাস্তবতা ও অস্তিত্বসংকটের এক বহুমাত্রিক মহাকাব্যিক আখ্যান। রবীন্দ্রনাথ এখানে বিধবা জীবনের নীরব আর্তনাদ, পুরুষের আত্মমোহী আকাঙ্ক্ষা, মাতৃত্বের সূক্ষ্ম আধিপত্য, প্রেমের দহন এবং অভিমানের গোপন ক্রীড়াকে এক অনন্য শিল্পশক্তিতে মূর্ত করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা উপন্যাসকে যে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ সেই ধারাকে রূপান্তরিত করেছেন আধুনিকতার অনন্য শিল্প-ঐতিহ্য হিসেবে। ফলে চোখের বালি কেবল রবীন্দ্রনাথের প্রথম আধুনিক উপন্যাসই নয়, বরং বাংলা সাহিত্যের অন্তর্জগতে আলো ও অন্ধকার, আকাঙ্ক্ষা ও বঞ্চনা, প্রেম ও বিরহের শাশ্বত দ্বন্দ্বের অনুরণন। কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বলেছিলেন, “রবীন্দ্রনাথ আমাদের অন্তরতম সত্তাকে শিল্পে রূপ দিয়েছেন, যা কেবল পড়ার জন্য নয়, অনুভব করার জন্য।” চোখের বালি সেই শিল্পানুভূতিরই অমোঘ দ্যুতি, যেখানে সমাজের দেয়াল ভেদ করে মানুষের হৃদয়ের চিরন্তন সত্য দীপ্ত হয়ে ওঠে।
কেতাব-ই’র মুদ্রিত বই,ই-বই এবং ব্লগজিন বিভাগের লেখালিখির নিয়মিত খোঁজখবর পেতে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যুক্ত হোন।
এই ব্লগজিনে প্রকাশিত সমস্ত লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব।